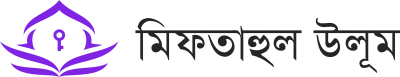বিশ্বাসের দর্শন
বিশ্বাসের দর্শন
১
আহ! কী শান্তি! ভাবতে কি যে ভালো লাগছে! ভাবতে ভালো লাগছে এ জন্যে, আমি একজন বিশ্বাসী। বিশ্বাসের জন্ম হয় আস্থা থেকে। আর আস্থা তৈরি হয় দীর্ঘ সময়ের পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে।
আমরা তাকে বিশ্বাস করি, যার উপর আমি ভরসা করতে পারি। আমি তাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য হই। তাকে বিশ্বাস করা ছাড়া আমার আর উপায় থাকে না। আমি তখন আর কোন যুক্তি প্রমান তালাশ করতে যাই না। আমার আস্থা যুগের পর যুগ অটুট থাকে। আমার বিশ্বাস দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হতে থাকে।
অবিশ্বাসের জন্ম সন্দেহ থেকে। সন্দেহ তৈরি করে আস্থার সংকট। সন্দেহ জন্ম দেয় মানসিক অস্থিরতার। এই অস্থিরতা জন্ম দেয় অবিশ্বাসের। কিন্তু সন্দেহ আর মানসিক অস্থিরতার এই টানাপোড়ন থেকে আর কখনও মুক্তি মিলে না।
আমার মা। আমি নিশ্চিত জানি তিনিই আমার মা। আমার মাকে আমি আমার বাবা ছাড়া আর কোন পরপুরুষের সাথে হেসে কথা বলতে দেখি নি। দেখি নি অন্য কারও সাথে ঘনিষ্ট হয়ে বসতে। বাবার অনুপস্থিতিতে অন্য কোন পুরুষের সাথে আড্ডা দিতে। যখন জানতাম না মানুষের জন্ম রহস্য, তখন থেকেই যা জেনে আসছি, এখনও তাই বিশ্বাস করি। আমার এই বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করার মতো কোন পরিস্থিতি তৈরি হয় না। তাই জন্মের রহস্যগুলো যখন থেকে বুঝে আসতে শুরু করে, তখনও এক পরম আস্থার কারনে কোন সন্দেহ দানা বাঁধার সুযোগ পায় না। তাই আমার আর প্রমান খুঁজে বেড়াতে হয় না। তাই ডিএনএ টেস্ট সম্পর্কে জানি। কিন্তু আমার কখনও নিজের ডিএনএ যাচাই করে দেখার কথা মনে হয় না। কারণ এই যে আমার বিশ্বাস এ তো এক পরম আস্থা থেকে জন্মলাভ করেছে। যাকে আর কোন পরিস্থিতি কখনও বদলাতে পারবে না।
এর বিপরীতে কেউ একজন ছোটবেলা থেকেই দেখে তাদের ঘরে পরপুরুষের আনাগোনা। সে প্রায়ই দেখে, যখন বাবা থাকে না, দু’তিনজন আন্কেল গভীর রাত পর্যন্ত তাদের বাসায় আড্ডা দিতে থাকে। এক পর্যায়ে সে ঘুমিয়ে যায়। তার দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ থেকে সে এটিও জানে, যে রাতে বাবা থাকেন, সে রাতে আঙ্কেলগন আসেন না। জন্মরহস্য বুঝার যে বয়স, তার আগে থেকেই তো সে জানে কে তার মা, কে তার বাবা। কিন্তু তার বাবা মায়ের মধ্যকার দূরত্ব, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের মাঝে ঝগড়া, তার মায়ের অাঙ্কেলদের সাথে মাখামাখি তার কচি অন্তরেও এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি করে।
এরপর যখন সে জন্মরহস্য বুঝতে পারার বয়সে উপনীত হয়, আর তার বাবার অনুপস্থিতিতে আঙ্কেলদের আনাগোনা আগের মতোই চলতে থাকে, আর এ সব মূহুর্তে তার উপস্থিতি তার মায়ের কাছে অপছন্দনীয় হওয়ার আভাস সে টের পায়, তার মধ্যে তৈরি হতে থাকে আস্থার সংকট। সন্দেহ তার অন্তরে দানা বাঁধতে থাকে। সে তখন ইচ্ছে করলেও আর তার মায়ের উপর আস্থা রাখতে পারে না। বিভিন্ন কানাঘুষা তার সন্দেহকে আরও উসকে দেয়। সে বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝে ঘুরপাক খায়। কখনও কখনও সে এটিও ভাবে, নিজের ডিএনএ একবার পরখ করে দেখবে কিনা। এভাবেই ধীরে ধীরে সে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অন্ধকারে ডুবে যেতে থাকে। তার না থাকে শান্তি, না থাকে স্বস্তি।
আলহামদুলিল্লাহ, আমার ভাবতে খুশীই লাগছে আমি বিশ্বাসী। সন্দেহ ও অবিশ্বাসের আযাব থেকে আমার রব আমাকে মুক্তি দিয়েছেন। তাই আমাকে কোন প্রমান তালাশ করতে হয় না। কারণ আমার এই বিশ্বাস গভীর এক আস্থার ফসল।
ইসলাম এমন এক ঈমানের কথা বলে, যা গভীর আস্থা থেকে তৈরি হয়। এই আস্থা পরম সত্যবাদী এক নবীর উপর। নবীগনকে আল্লাহ তায়ালা এভাবেই তৈরি করেন। নবীর নবুওয়ত-পূর্ব জীবন বার বার এ কথা বলতে থাকে, ইনি মিথ্যা বলতে পারেন না। তাই আবু বকরেরা এক বাক্যেই ঈমান নিয়ে আসেন। এবং এই সত্যবাদী নবীর সাথে চলতে চলতে এই আস্থা বাড়তে থাকে। তাঁরা এই নবীকে দেখতে থাকেন সহজ ও কঠিন সর্ব অবস্থায়। দেখেন বিপদে-আপদে, যুদ্ধের মূহুর্তে। সবসময় তাঁকে একই রকম পান। ফলে আস্থায় কখনও চিড় ধরে না। বরং দিনে দিনে তা বাড়তে থাকে।
তাবেয়ীগন সাহাবাদের দেখেন। তাদের মুখে শুনেন এক সত্য নবীর গল্প। আর তাদের জীবনেও পেতে থাকেন সত্য নবীর অটুট অনুসরণ। যে সততার গল্প তারা শুনান, সে সততা দেখতে পাওয়া যায় তাদের জীবনে, পরিপূর্ণ মাত্রায়। ফলে সাহাবাদের সততা দেখে তাঁরা নবীর সততাকে আন্দাজ করেন। আর যুগে যুগে এভাবেই চলতে থাকে। সততার এই চেইনে যারা আসেন, তাই তাদের অন্তরে কখনও সন্দেহ দানা বাঁধে না। তারা যে যুগ যুগ ধরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই সত্যকে বার বার পর্যবেক্ষণ করেন। যুগ যুগ ধরে চলমান এই পর্যবেক্ষণ যে কোন প্রকার বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের চেয়ে অনেক বেশি মজবুত। তাই তাদের কোন রেট্রোস্পেকটিভ পর্যবেক্ষণের দ্বারস্থ হতে হয় না। তাদের এই প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণকে তাই বিবর্তন বা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মতো কিছু রেট্রোস্পেকটিভ পর্যবেক্ষণ চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে না। এই রেট্রোস্পেকটিভ পর্যবেক্ষণ দ্বারা কেবল তারাই প্রতারিত হয়, যারা সন্দেহের বাতিকগ্রস্ত, যাদের নিজেদের উপরও এক ফোঁটা আস্থা নেই। এরা বড় অস্থির। নিজেও অস্থিরতার আযাবে দংশিত হতে থাকে,অন্য আরও অনেককে টেনে আনে অস্থিরতার এই আযাবে।
এই আযাব কেবল দ্বিগুন তিনগুন হয়ে বাড়তে থাকে। এ থেকে সহজে এদের নিস্তার নেই।
২
সন্দেহ থেকেই সুত্রপাত হয় অবিশ্বাসের। আর সন্দেহ তখন অন্তরে দানা বাঁধে, যখন নিশ্চিত জ্ঞান সামনে থাকে না। নিশ্চিত জ্ঞান এমন এক বিশ্বাস তৈরি করে, যা কখনোই অন্ধ নয়। ইসলাম কোন অন্ধবিশ্বাসের দিকে ডাকে না। ঈমান বিল গায়েব বলতে কোন অন্ধবিশ্বাসকে বুঝায় না, বরং ইলমে ওহীর দ্বারা অন্তর আলোকিত হওয়ার মাধ্যমেই ঈমান তৈরি হয়। সূর্যপূজা, অগ্নিপূজা, মূর্তিপূজা ইত্যাদি যে গুলোর পক্ষে কোন নিশ্চিত জ্ঞান নেই, সে গুলোর ভিত্তি অন্ধবিশ্বাসের উপর হতে পারে, কিন্তু যে অন্তর ইলমে ওহীর আলোতে আলোকিত সে অন্তরে তৈরি হয় এক উপলদ্ধির, যা কোনভাবেই টলে না। এরই নাম ঈমান বিল গায়ব।
আসমানী ইলম এবং সাথে একজন নবীর উপস্থিতি সবার অন্তরে হককে স্পষ্ট করে তোলে। কেউ হয়তো তার দুনিয়াবী কোন স্বার্থ, কিংবা অহংকারের কারনে হককে কবুল করে না, কিন্তু তার অন্তরেও স্পষ্ট হয়ে যায় ইনি নবী।
আল্লাহর রাসুল যখন দাওয়াত দেয়া শুরু করলেন, কেউ তাকে কবি, কেউ যাদুকর, কেউ গনক বললো ; কিন্তু ধীরে ধীরে সবাই উপলদ্ধি করলো ইনি মোটেই যাদুকর, কবি বা গনক নন।
নবীর মূজিযা, আখলাক, ধীরে ধীরে সর্বত্র তাঁর প্রাধান্যলাভ করা সবাইকে বুঝিয়ে দেয় তাঁর দাবি মোটেই মিথ্যে নয়।
আল্লাহর রাসুল যখন এভাবে তাঁর দাওয়াতকে পেশ করে চললেন, তখনকার ইহুদী, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক সবার কাছে হক স্পষ্ট হয়ে গেলো, চাই সবাই কবুল করুক আর না করুক।
এরপর অতি অল্প সময়ের মধ্যে সর্বত্র ইসলামের জয়জয়কার, দীর্ঘদিনের মানবিক সমস্যাগুলোর সমাধান হওয়া, এক উন্নত জীবনে অভ্যস্ত হওয়া এক জাতি তৈরি হওয়া সবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় ইসলামের এই নূর মহান স্রষ্টা পক্ষ থেকে এসেছে। স্বাভাবিকভাবেই তা স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করতে থাকে দয়ালু, সর্বশক্তিমান এক মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব।
আজ নব্য নাস্তিকেরা বার বার ইসলামের এই বিজয়গাঁথাকে অস্বীকার করতে চায়, চরিত্রের সেই চরম উৎকর্ষকে পাশ কাটিয়ে যায়, হাজার বছরের জমানো সমস্যাগুলোর যে সমাধান ইসলাম দিয়েছে তা মোটেই উচ্চারন করে না। কারন এতে তাদের বড় ভয়।
সমস্ত অবিশ্বাসকে লালন করার জন্যে অবিশ্বাসীরা একজোট। সারা বিশ্বে এরা একটা কমন প্লাটফর্ম ব্যবহার করে। এরা এদের পূঁজি হিসেবে ব্যবহার করে ডারউইনিজমের মতো একটা মৃত মতবাদকে। হ্যাঁ ডারউইনিজম একটা মৃত মতবাদ। এটি এর সমস্ত বৈজ্ঞানিক গ্রহনযোগ্যতা হারিয়েছে অনেক আগেই। কিন্তু বিবর্তনবাদীরা একে বার বার নানা ঢঙ্গে, নানা রঙ্গে প্রকাশ করে এটিকে জীবিত রাখার চেষ্টা করছে। এবং নাস্তিক্যবাদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে এটিই এদের বড় অস্ত্র।
অবিশ্বাসীরা উনিশ শতকের আগে ভালো কোন অস্ত্র হাতে পায় নি। ডারউইনিজমই এদের অনুকূলে সর্বপ্রথম কার্যকর অস্ত্র হিসেবে প্রকাশ পায়। আসলে ডারউইনবাদ তো বস্তুবাদের একটা বৈজ্ঞানিক পোষাক মাত্র। বিবর্তনবাদ বস্তুবাদের সবচেয়ে সফল অস্ত্র। তাই এটিকে এরা মরতে দিতে চায় না। এই অস্ত্রটিকে ব্যবহার করেই এরা সারা পৃথিবীতে যুবক সমাজকে বিভ্রান্ত করছে। এই বিবর্তনবাদীরা সারাবিশ্বে পাচ্ছে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা। বিবর্তনবাদ না মানলে তো কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার সুযোগই পায় না বিজ্ঞানীরা। কোন বিজ্ঞানীকে আস্তিক জানলে তাকে কাজ করার সুযোগই দেয়া হয় না। তাই অবিশ্বাসীদের এই অস্ত্র সম্পর্কে আমাদের ভালোভাবে জানতে হবে।
আমাদের দেশে গত দশকে ওরা এই বিতর্বনবাদকে পূঁজি করেই যত অপতৎপরতা চালিয়েছে। শত শত তরুনকে বিভ্রান্ত করেছে। অবিশ্বাসের দর্শন ইত্যাদি বইতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরিভাষাকে ব্যবহার করে এই বিবর্তনবাদকেই ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। এই এক মতবাদ দিয়েই নানা ঢঙ্গে মগজ ধোলাইয়ের কাজ চলেছে।
একদিকে বিজ্ঞানমনস্কতার বেশ ধরে ওরা মগজধোলাই করেছে, অন্যদিকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়কে টার্গেট বানিয়ে ঠাট্টা-তামাশা ও পরিহাসের মাধ্যমে ধর্মের আজমত খতম করার চেষ্টা করেছে।
ওরা বার বার চেষ্টা করেছে এ কথা প্রতিষ্ঠিত করার -ডারউইনবাদকে অস্বীকার করা মানে বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা, বিবর্তনবাদ অস্বীকার করা মানে বিজ্ঞানের একটা প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অস্বীকার করা। বাস্তবে তা নয়।
বাংলাদেশে হেফাজতে ইসলামের গনজাগরনের কারনে ওদের তৎপরতা হঠাৎ মুখ তুবড়ে পড়েছে, যা তারা কল্পনাই করতে পারে নি। নাস্তিক্যবাদের বিরুদ্ধে এভাবে পুরো জাতির এক সাথে ফুঁসে উঠা আমাদের অনেক বড়ো বিজয়। এতটুকুও আমাদের অনেক বড়ো অর্জন।
এখন আমাদের ওদের মূলে আঘাত হানতে হবে। ভালভাবে প্রমান করে দিতে হবে বিবর্তনবাদের অসারতা। এটি নিয়ে এত বেশি জানতে হবে যেন আমরা ওদের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা শুনে ভড়কে না যাই। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকেই ওদের লা জাওয়াব করে দিতে হবে।
আফসোস হলো, আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানের প্রতি দূর্বল ঠিকই, কিন্তু বিজ্ঞান জানে কম। এই সুযোগটাই ওরা নিয়েছে। বিজ্ঞানের মোড়কে ওরা তরুনদের বিভ্রান্ত করেছে।
এখনই সময় ওদের মুখোশ খুলে দেয়ার। কিন্তু আফসোস! আমাদের প্রিপারেশন যে বড়ো অপ্রতুল!
৩
মানুষের চোখ দেখে দমে গিয়েছিলেন চার্লস ডারউইন। কারন এমন একটা কমপ্লেক্স অঙ্গ তো আর তার থিওরী অনুসারে গঠিত হতে পারে না।
আসলে ডারউইন তার নিজস্ব কিছু পর্যবেক্ষণ থেকে বলেছিলেন, সেই এককোষী জীব থেকে সমস্ত জীবের জন্ম। দীর্ঘ সময় ধরে ধীরে ধীরে বিবর্তনের মাধ্যমে সমস্ত প্রাণীগুলো সৃষ্টি হয়েছে। তিনি আশা করেছিলেন, অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা তা প্রমান করবেন। তার আশা ছিল ফসিলের পর ফসিল আবিষ্কৃত হবে, কি করে ধীরে ধীরে এককোষী প্রাণী থেকে জটিল, বহুকোষী প্রাণীগুলো সৃষ্টি হলো তার একটা ব্যাখ্যা দেয়া যাবে। কিন্তু হঠাৎ করে ক্যামব্রিয়ান যুগের এমন সব ফসিল আবিষ্কৃত হতে লাগলো, যারা প্রায় প্রত্যেকটিই জটিল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট। প্রাক ক্যামব্রিয়ান যুগে কেবলই কিছু এক কোষী জীবের ফসিল পাওয়া গিয়েছিলো। এখন এক কোষী প্রাণী থেকে হঠাৎ এত বেশি বহুকোষী জীব কিভাবে গঠিত হলো তার ব্যাখ্যা দেয়া কঠিন হয়ে পড়লো। আর বিবর্তনের মধ্যবর্তী ধাপগুলোর ফসিলও অনেক বেশি পাওয়া যাওয়ার কথা, কিন্তু তা পাওয়া গেলো না। ফলে কিভাবে এক কোষী প্রাণী থেকে নতুন নতুন জটিল বহুকোষী প্রাণী তৈরি হলো, বিবর্তনবাদের মাধ্যমে তা ব্যাখ্যা করা গেলো না। ফলে মাত্র দেড় শতাব্দীর মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়লো ডারউইনিজম। ক্যামব্রিয়ান যুগে হঠাৎ এত বেশি জটিল বহুকোষী প্রাণীর আবির্ভাব তাদের বাধ্য করলো ক্যামব্রিয়ান যুগটিকে নতুন ভাবে ব্যাখ্যা করতে। তার এর নাম দিলো বায়োলজিক্যাল বিগব্যাঙ।
অথচ এই ফেইল্ড মতবাদটাই নাস্তিকদের আসল ভরসা।
এরা ইনিয়ে বিনিয়ে, বিভিন্ন কাল্পনিক স্টেইজ বর্ণনা করে বিবর্তনবাদ নামক একটা অবাস্তব থিওরীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু কিছু প্রশ্ন টেকনিক্যালি এড়িয়ে যায়।
যদি প্রশ্ন করা হয়, প্রানের শুরু কিভাবে হলো? কিন্তু বিবর্তনবাদীদের কাছে এ প্রশ্নের জবাব নেই। ওরা বিভিন্ন বড় বড় বুলি আওড়িয়ে অবশেষে বলবে, এর জন্য কোন স্রষ্টার প্রয়োজন নেই। মহাবিশ্বের সূচনা নিয়েও ওরা অস্বস্তিতে ভূগে।কারন মহাবিশ্বের সূচনা সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করান। তাঁরা সর্বোচ্চ এভাবে বলতে পাররেন, সম্ভবত এভাবে মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে। তারা কখনও এভাবে বলতে পারেন না, এভাবেই মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে। তাই নাস্তিকেরা বিভিন্ন ধরনের আজগুবী ব্যাখ্যা হাজির করে অবশেষে বলবে, এর জন্যও স্রষ্টার কোন প্রয়োজন নেই।
যদি প্রশ্ন করা হয়, মানলাম বিবর্তনের মাধ্যমেই এককোষী থেকেই সব বহুকোষী জীবের উদ্ভব হলো, কিন্তু মধ্যবর্তী স্তরগুলোর মধ্য দিয়েই তো সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছে, তাহলে মধ্যবর্তী হাজার হাজার স্টেইজের ফসিল পাওয়া যাওয়ার কথা সেগুলি নেই কেন।
ওদের কাছে এর কোন জবাব নেই।
আশ্চর্য কথা হলো, নাস্তিক্যবাদকে প্রমান করার জন্য ওরা কঠিন কঠিন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আওড়িয়ে সেই পুরোনো কাসুন্দিই গাইতে থাকে।
অভিজিত রায় ‘ অবিশ্বাসের দর্শণ ‘ বইয়ে এভাবেই পুরোনো গীত গেয়েছে। আর এ সব পড়েই হুজুগে বাঙ্গালীর জোয়ান ছেলেগুলো নিজেকে বানর কিংবা হনুমান অথবা শিম্পাঞ্জীর উত্তরপুরুষ ভাবা শুরু করেছে।
আপনি কল্পনা করুন তো, এর পরিণতি কত ভয়াবহ? কিছু মানুষ নিজেকে জন্তু জানোয়ারের উত্তরপুরুষ ভাববে আর কোন নৈতিকতার ধার ধারবে এটা কি হতে পারে? তাই এরা পশুর মতো যা ইচ্ছে করতে চায়। সারভাইভ্যাল ফর দি ফিটেস্ট বলে গায়ের জোরে অন্যকে পদানত করে নিজেকে টিকিয়ে রাখতে চায়। ফলে মানবতা পড়ে হুমকির মুখে। মানুষ আর জানোয়ারে আর কোন পার্থক্য থাকে না।
৪
চার্লস ডারউইন।
তিনি উনিশ শতকের মানুষ। সেই ১৮৩০ কিংবা ১৮৪০ সালে তিনি আর কতটুকুই বা জানতেন। তখন মানুষ সর্বোচ্চ এতটুকু জানতো, জীবকোষ মানে পানিভর্তি একটা কোষ, যা একটা চামড়া দিয়ে ঘেরা। কোষের ভেতরে কি আছে, তা জানার কোন উপায় মানুষের ছিলো না। কিন্তু যখন বিংশ শতকে মানুষ ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ বানালো, দেখতে সক্ষম হলো কোষের ভেতর কি আছে। মানুষ জীবকোষের ভেতরের অঙ্গানুগুলো দেখলো। আস্তে আস্তে আবিস্কার হলো ক্রোমোজোম, এরপর এর ডিএনএ সিকোয়েন্স, এরপর যা আবিস্কার হলো, তাকে তো মিরাকল ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।
মানুষ জানলো, একটা ডিএনএ মলিকিউলের ভেতর কি পরিমান তথ্য আছে।
আজ আমরা জানি। আমরা জানি, একটা ডিএনএ অনু এত বেশি তথ্য ধারন করে, যা দিয়ে মিলিয়ন পৃষ্ঠার একটা এনসাইক্লোপেডিয়া লিখা যায়। একটা ডিএনএ অনুর তথ্য লিখলে ভরে যাবে ১০০০ বই। আজ আমাদের সামনে আছে তেইশ ভলিউমের এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা, যার পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৫০০০, যা কিনা তথ্যভান্ডারের বিশাল খনি।
আপনি কল্পনা করুন তো, এই এনসাইক্লোপেডিয়ার চেয়ে চল্লিশগুন বড় তথ্যখনি হচ্ছে একটা ডিএনএ অনু, যা নিয়ন্ত্রন করে মানুষের দৈর্ঘ্য, গায়ের রঙ, তার উচ্চতা, তার স্বভাব, তার ভবিষ্যতে যে রোগগুলো হতে পারে তার তথ্য ইত্যাদি। আরও আশ্চর্য কথা হলো, এত বেশি তথ্য আছে এমন একটা জীবকোষের নিউক্লিয়াসে, যে কোষটির দৈর্ঘ্য এক মিটারের বিনিয়নভাগের একভাগ। সেই নিউক্লিয়াসটি তো জীবকোষের তুলনায় কত বেশি ক্ষুদ্র। বিজ্ঞানীরা আজ বলছেন, একটা ডিএনএ অনুর তথ্যগুলো যদি কাগজে লিখা হয়, কাগজটি বিছানো হলে সেটি পৌঁছে যাবে উত্তর মেরু থেকে ইকুয়েডর পর্যন্ত।
এত কিছু তো আর চার্লস ডারউইন জানতেন না। জানলে কি তিনি কিছু প্রাণীদের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে এ কথা বলতেন, কোন বুদ্ধিমান অথরিটি নয়, বরং অটোমেটিক্যালি ধীরে ধীরে এককোষী প্রাণী থেকে সৃষ্টি হয়েছে এত সব জটিল সব প্রাণীগুলো ।
তিনি জানতেন না, বাহ্যিক পরিবর্তনগুলো হতে হলে আগে হতে হবে কোষের ভেতরে জেনেটিক পরিবর্তন। এক এক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনের জন্য কত বিলিয়ন বিলিয়ন পরিবর্তন সাধিত হতে হবে জীনের ভেতর।
তিনি কেবল বাহ্যিক পরিবর্তনগুলো খেয়াল করেছেন। যেমন, লেজযুক্ত একটা প্রাণীর ধীরে ধীরে অভিযোজনের মাধ্যমে লেজ খসে যাওয়া, কিংবা একটা মাছের একটা টিকটিকিতে পরিণত হওয়া। তিনি জানতেন না, এর চেয়ে আরও ক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য কত ঝড় বয়ে যাবে জীনের ভেতরে।
আমি নিশ্চিত, এত কিছু জানা থাকলে কখনও ডারউইন এই কথা বলতেন না। কিভাবে তিনি তা বলবেন?
তিন শব্দের একটা বাক্য অটোমেটিক্যালি লিখা হতে পারে না। মাত্র ক্ষুদ্রতম একটা কোষের আরও ক্ষুদ্রতম ক্রোমোজোমের ভেতরে এত তথ্য কে সন্নিবেশিত করে রাখলো এটা কি কখনও কো-ইনসিডেন্স হতে পারে?
আমার আশ্চর্য লাগে, এ কেমন বিজ্ঞানমনস্কতা? এত বেশি স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও কি করে কিছু মানুষ উনিশ শতকের এক ভুল চিন্তাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারে? এটিই তো অন্ধবিশ্বাস, এটিই তো অপ-বিশ্বাস।
ব্যস, এখানে এসে আমার আবেগ বাঁধনহারা হয়ে পড়ে। আমি আর স্থির থাকতে পারি না। ইচ্ছে করে লুটিয়ে পড়ি সিজদায়। নতুন করে বার বার চিনছি আমার স্রষ্টাকে। আমার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে,
ربنا ما خلقت هذا باطلا
سبحانك فقنا عذاب النار
হে আমার রব! তুমি এ সব অনর্থক সৃষ্টি কর নাই। আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি, আমাকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করো।
এক লোক কেবল আকাশ দেখে এ কথা বলেছিলো, তার মাগফিরাত হয়ে গেলো। একজন আধুনিক মানুষের তো তা হাজার বার বলা দরকার। আমি কি করে ভুলে থাকি এমন এক নিপূণ স্রষ্টাকে।
৫
কিছুক্ষণের জন্য আমরা ‘অসম্ভব’ শব্দটিকে ভুলে যাই।
ধরা যাক, খুবই অনুপযোগী ও বিশৃঙ্খল এক পরিবেশে একদম কাকতালীয়ভাবে গঠিত হলো একটা প্রোটিন অনু। পৃথিবীর সেই শৈশবে যখন পরিবেশ আসলেই ছিলো অস্থির, বিশৃঙ্খল।
এই প্রোটিন অনুটি সেই অস্থির পরিবেশে অপেক্ষা করতে লাগলো অনাগত প্রোটিন অনুর জন্যে। অবশেষে আবার ‘বাই চান্স’ কাকতালীয় ভাবে তৈরি হলো দ্বিতীয় প্রোটিন অনু। আর একদম প্রথমটির পাশে বসে গেলো। সেই প্রতিকূল পরিবেশে সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে প্রোটিন অনুগুলো অপেক্ষা করতে লাগলো বছরের পর বছর আল্ট্রা ভায়োলেট রে ও অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাবকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে। তারপর মিলিয়ন মিলিয়ন প্রোটিন অনু এভাবে এক এক করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গঠিত হতে লাগলো এবং সুশৃঙ্খলভাবে একের পাশে এক বসে যেতে লাগলো অটোমেটিক। আর এভাবেই তারা তৈরি করতে লাগলো একটা অর্থবহ কম্বিনেশন আর তৈরি হতে লাগলো জীবকোষের অঙ্গানুগুলো। বাইরের কোন বস্তু, ক্ষতিকর কোন অনু, অপ্রয়োজনীয় কোন প্রোটিন চেইন তাদের কাজে কোন ব্যাঘাত ঘটাতে পারলো না।
তারা এভাবে সৌহার্দপূর্ণ পারস্পরিক এক সংযোগ তৈরি করলো এবং প্রয়োজনীয় এনজাইমগুলোকেও নিজেদের কাছাকাছি সন্নিবেশিত করলো। তারপর তারা নিজেরা নিজেরাই একটা মেমব্রেন (পর্দা) দিয়ে ঘিরে নিলো আর আর ভেতরটাকে পরিপূর্ণ করে নিলো এমন এক বিশেষ তরল দিয়ে যা তাদের জন্য একটা আদর্শ পরিবেশ তৈরি করে।
ধরে নিলাম, এ সব খুব বেশি অসম্ভব ইভেন্টগুলো আসলেই ‘বাই চান্স’ সম্ভব হয়ে গেলো, তারপরও কি এই অনুপুঞ্জ সম্মিলিতভাবে প্রানের আবির্ভাব ঘটাতে পারে?
উত্তর হচ্ছে ‘না’।
কারন হাজার হাজার গবেষণা দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে, জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক সব উপাদান এক জায়গায় জমা হয়ে গেলেও জীবনের সূচনা করা যায় না। জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় সব প্রোটিনগুলো সংগ্রহ করা গেলো, সেগুলোকে একটা টেস্টটিউবে নিয়ে হাজার চেষ্টা করেও কি একটা জীবন্ত কোষ তৈরি করা সম্ভব?
বিজ্ঞানীরা এর জন্য কম আয়োজন করেন নি। কিন্তু বারে বারে ব্যর্থ হয়েছে তাদের এই চেষ্টা। সমস্ত পর্যবেক্ষণ ও এক্সপেরিমেন্ট দ্বারা এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে, জীবনের উৎপত্তি কেবল জীবন থেকে সম্ভব।
জড় বস্তু থেকেই জীবনের উদ্ভব হয়েছে, যাকে বলা হচ্ছে ‘এবায়োজেনেসিস’ -তা কেবলই একটা অবাস্তব গল্প, যার অস্তিত্ব শুধু বিবর্তনবাদীদের স্বপ্নে সম্ভব।
পৃথিবীতেও জীবনের অস্তিত্ব কেবল জীবন থেকেই হয়েছে। চিরঞ্জীব মহান স্রষ্টা থেকেই প্রানের উদ্ভব। জীবন শুরু হয়, চলতে থাকে এবং শেষ হয় কেবলই তাঁর ইচ্ছায়। কারন তিনি ‘হাইয়্যুন, লা ইয়ামুত’। তিনিই সমস্ত প্রানের উৎস।
বিবর্তন কোন ভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারে না জীবন কিভাবে শুরু হলো, আর কিভাবেই বা প্রানের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদানগুলো তৈরি হলো এবং সুশৃঙ্খলভাবে একত্রিত হলো। কাকতালীয়ভাবে যে এটি কখনও হতে পারে না তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট।
পৃথিবীর মানুষ কখনোই সক্ষম হবে না প্রান সৃষ্টি করতে আর কখনও উদ্ধারও করতে পারবে না প্রানের রহস্য। আর স্রষ্টাও তা কখনো, কোন কিতাবেই মানুষকে জানান নি। কেবল সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন, প্রান কেবল আমার হুকুম।
يسئلونك عن الروح، قل الروح من امر ربي.
তারা আপনাকে প্রান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, বলুন প্রান আমার রবের হুকুম।
প্রানের শুরু কোন থিওরী, কোন মতবাদ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। কেবল অসহায়ভাবে মেনে নিতে হবে, পরম ক্ষমতাবান কেউ প্রানের সৃষ্টি করেছেন। বিবর্তন নয়, বরং সৃষ্টিত্ত্বই এর প্রকৃত গ্রহনযোগ্য ব্যাখ্যা।
এ জন্যই কার্ডিফ ইউনিভার্সিটির ডঃ চন্দ্র বিক্রমাসিংহে বড় অসহায়ভাবে প্রকৃত বাস্তবতাকে স্বীকার করেছেন, যিনি সারা জীবন বলে এসেছেন, হঠাৎ করে একটা কো-ইনসিডেন্স এর মাধ্যমে জীবনের উদ্ভব ঘটেছে।
তিনি বলেন,
From my earliest training as a scientist, I was very strongly brainwashed to believe that science cannot be consistent with any kind of deliberate creation. That notion has had to be painfully shed. At the moment, I can’t find any rational argument to knock down the view which argues for conversion to God. We used to have an open mind; now we realize that the only logical answer to life is creation-and not accidental random shuffling. (Chandra Wickramasinghe, Interview in London Daily Express, 14 August 1981)
“বিজ্ঞানী হিসেবে আমার একদম প্রাথমিক ট্রেনআপের সময় থেকে আমি এই বিশ্বাসের উপর শক্তভাবে ব্রেইনওয়াশ্ড ছিলাম যে, কোন স্রষ্টার ইচ্ছাধীন পরিকল্পিত সৃষ্টিতত্ত্ব কখনোই বিজ্ঞানেরসাথে সংগতিপূর্ণহতে পারে না। কিন্তু খুবই দুঃখজনকভাবে আমাকে এ ধারণা পরিত্যাগ কররতে হয়েছে। এই মূহুর্তে স্রষ্টার সৃষ্টিতত্ত্ব ধারনার বিরুদ্ধে পেশ করার মতো কোন যুক্তি আমি খুঁজে পাই না। আমাদের একটা খোলা মন থাকা উচিত ছিলো। এখন আমরা উপলদ্ধি করি, জীবনের একমাত্র যৌক্তিক উত্তর হচ্ছে সৃষ্টিতত্ত্ব, জীবন কখনোই কোন এলোপাথাড়ি এক্সিডেন্টাল শাফলিং এর ফসল নয়।
( ডঃ চন্দ্র বিক্রমাসিংহে, সাক্ষাৎকার, লন্ডন ডেইলি এক্সপ্রেস, ১৪ আগস্ট, ১৯৮১)
হে আমার মাওলা, আমি বার বার তোমাকে চিনি, তোমার নতুন পরিচয় আমাকে বারে বারে শিহরিত করে। আমার দৃষ্টি কেবল খুলতে থাকে, খুলতে থাকে। এখন আমি সর্বত্র তোমার উপস্থিতি খুঁজে পাই।
৬
আপনি একটি কার মরুভূমিতে রেখে এলেন। দীর্ঘ একটা বছর সেটি মরুভূমিতে পড়ে রইলো। এক বছর পরে আপনি গিয়ে কি দেখবেন?
গাড়িটি ঠিক আগের মতোই আছে?
আপনি দেখলেন, গাড়িটি বিবর্ণ হয়ে গেছে। ভেঙ্গে গেছে গাড়ির কাচ। ফুটো হয়ে গেছে গাড়ির চাকা। নষ্ট হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গেছে ইঞ্জিন।
আপনি ভাবছেন, এমন হওয়ার তো কথা না। কেউ তো এসে গাড়িটিকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে নি। কেউ এসে চাকা পাংচার করে দিয়ে যায় নি। এই মরুভূমিতে কে এসে তা করবে!
আসলে আপনি যা দেখছেন, তাই বাস্তব। এ পৃথিবীতে যে কোন বস্তু ফেলে রাখলে চাই সেটি জীবিত হোক, বা মৃত; সেটি ক্ষয়ে যাবে, বিবর্ণ হবে, নষ্ট হবে, বিকল হবে। এটিই নিয়ম।
এটিই বলে থার্মোডাইনেমিক্স এর দ্বিতীয় সুত্র। যেটি কিনা পদার্থবিদ্যার সর্বজন গ্রহনযোগ্য বেসিক সুত্রগুলোর অন্যতম।
সুত্রটি বলে, পৃথিবীর যে কোন সিস্টেমকে স্বাভাবিক অবস্থায় ছেড়ে দিলে সাধারন অবস্থায় সেটি ক্ষয়প্রাপ্ত হবে, নষ্ট হবে, বিঘ্নিত হবে। আর এই নষ্ট হওয়ার পরিমান অতিক্রান্ত সময়ের সমানুপাতিক। সুত্রটির অপর নাম ‘ল অব এনট্রপি’। এনট্রপি বলা হয় কোন বস্তু বা সিস্টেমের ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার, নষ্ট হওয়ার, ত্রুটিযুক্ত হওয়ার পরিমানকে।
সুত্রটি থিওরোটিক্যাল ও এক্সপেরিমেন্টাল উভয় দিক দিয়ে বার বার প্রমানিত হয়েছে। এটি একটি বাস্তব সত্য, এর অন্যথা হওয়ার নয়।
সিস্টেমটি যত ডিসঅর্ডার্ড হবে, যত ডিসঅর্গানাইজ্ড হবে, এনট্রপির পরিমান হবে তত বেশি। এই সুত্র বলছে, এই মহাবিশ্ব ধীরে ধীরে সময়ের বিবর্তনের সাথে ধ্বংসের দিকে, ক্ষয়ের দিকে, বিশৃঙ্খলতার দিকে চলেছে।
আলবার্ট আইনস্টাইন এই সুত্রকে বলেছেন ‘primier law of all science’.
বিবর্তনবাদ থার্মোডাইনেমিক্স এর এই দ্বিতীয় সুত্রের সম্পূর্ণ উল্টো। বিবর্তনবাদ বলে, কতগুলো বিচ্ছিন্ন, মৃত পরমানু ও অনু সময়ের সাথে পাশাপাশি বিন্যস্ত হবে, অর্গানাইজ্ড হবে, সুশৃঙ্খল হবে, কাকতালীয়ভাবে পরস্পর মিলিত হয়ে সুগঠিত প্রোটিন, ডিএনএ, আরএনএ তৈরি হবে এবং আরও বিন্যস্ত হয়ে তৈরি হবে জীবকোষের জটিল সব অঙ্গানু। শুধু কি তাই? এরপর আরও বিন্যস্ত হয়ে এককোষী থেকে বহুকোষী, সরল থেকে জটিল, জটিল থেকে জটিলতর প্রাণীতে পরিণত হবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত, বিচ্ছিন্ন কতগুলো বস্তু কেবলই প্রাকৃতিকভাবে দিন দিন বিন্যস্ত, সুগঠিত, উন্নততর অবস্থার দিকে এগুবে। যা একটা প্রতিষ্ঠিত ও পরীক্ষিত সুত্রের সরাসরি বিপরীত।
কিন্তু বিবর্তনবাদীরা বলতে চান, যেমন জেরিমি রিফকিন বলেছেন, বিবর্তনের ক্ষেত্রে এটি ঘটেছে একটা ম্যাজিকেল পাওয়ার অর্জনের মাধ্যমে। কি আশ্চর্য বিশ্বাস, যা কেবল এ সমস্ত বিবর্তনবাদীদের স্বপ্নে সম্ভব।
দেখুন এরা কেমন অন্ধবিশ্বাসী, কিভাবে স্পষ্ট সায়েন্সকে বাদ দিয়ে এরা একটা ডগমেটিক বিলিফকে আঁকড়ে ধরে।
এরা কিন্তু বিবর্তনবাদ যে বেসিক সুত্রের বিপরীত হয় তা জানেন। তাই নিজেদের বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে ক্লোজ্ড সিস্টেম আর ওপেন সিস্টেম এর ধারনার অবতারণা করেন।
তারা বলেন, এই সুত্র প্রযোজ্য হবে কেবল ক্লোজ্ড সিস্টেমের ক্ষেত্রে। পৃথিবী তো একটা ওপেন সিস্টেম। কারন প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে সৌরশক্তির প্রবাহ জারি রয়েছে। তাদের ধারনা, সৌরশক্তির ধারাবাহিক প্রবাহের কারনে বিবর্তনের ক্ষেত্রে ক্ষয় বা লয় ঘটার মতো কোন ঘটনা ঘটবে না।
অথচ তাদের এ ব্যাখ্যায় রয়েছে মারাত্মক ত্রুটি। কারন কোন সিস্টেম বিন্যস্ত হওয়ার জন্য কেবল শক্তির নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহই যথেষ্ট নয়। বরং এর জন্য থাকতে হবে সুনির্দিষ্ট মেকানিজম, যা শক্তিকে ক্রিয়াশীল করবে।
যেমন, একটা কারের মধ্যে একটা ইঞ্জিন, একটা ট্রান্সমিশন সিস্টেম, একটা নিয়ন্ত্রক মেকানিজম থাকতে হয় পেট্রোলের শক্তিকে কাজে পরিণত করার জন্য। এই রূপান্তর পদ্ধতি ছাড়া কখনোই কার পেট্রোলের শক্তিকে কার্যকর শক্তিতে পরিণত করতে পারবে না।
জীবনের ক্ষেত্রেও ঠিক একই নিয়ম প্রযোজ্য। এ কথা সত্য প্রাণ সূর্য থেকে শক্তি পায়। কিন্তু সৌরশক্তিকে মেকানিক্যাল শক্তিতে পরিণত করার জন্যে একটা কার্যকর, জটিল রূপান্তর পদ্ধতি থাকতে হয়।
যেমন উদ্ভিদের মধ্যে ফটোসিনথেসিস, প্রানীদের ক্ষেত্রে খাদ্য থেকে শক্তি নিঃসরনের জন্য ডাইজেস্টিভ এবং মেটাবলিক সিস্টেম।
কোন প্রাণীই এই শক্তি রূপান্তর সিস্টেম ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। এই ধরনের একটা রূপান্তর পদ্ধতির উপস্থিতি ছাড়া সূর্যতাপ কেবলই একটা ধ্বংসাত্মক শক্তি, যা পুড়াবে, গলাবে, ধ্বংস করবে।
বুঝা গেলো সৌরশক্তির প্রবাহ বিবর্তনের জন্য সহায়ক হবে কেবল তখনই, যখন একটা শক্তি রূপান্তর পদ্ধতি উপস্থিত থাকবে, চাই সিস্টেম ক্লোজ্ড হোক, বা ওপেন।
এ কথা স্পষ্ট সেই পৃথিবীর শৈশবে, এমন একটা শক্তি রূপান্তর পদ্ধতির অনুপস্থিতিতে, সৌরশক্তিকে কার্যকর করার কোন মেকানিজমের অনুপস্থিতিতে কিভাবে সম্ভব বিবর্তনের মতো ঘটনা ঘটা, যা ধীরে ধীরে জটিল থেকে জটিলতর, অবিন্যস্ত থেকে বিন্যস্ত, অগোছালো থেকে সাজানো অবস্থার দিকে নিয়ে যাবে সচেতন কোন ডিজাইন ও পরিকল্পনা ছাড়া?
উত্তর একটাই প্রানের উদ্ভব কোন কাকতালীয়, হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পিত, উদ্দেশ্যমন্ডিত, সচেতনভাবে সম্পন্ন, যাকে এক কথায় বলতে হয় সৃষ্টি, যা এক মহান স্রষ্টারই কারিশমা।
৭
এক বিখ্যাত ফার্মাসিউসিটিক্যাল কোম্পানির ঔষধ ফ্যাক্টরি। বিভিন্ন প্লান্টে কাজ করছেন বেশ কয়েকজন দক্ষ ফার্মাসিস্ট এন্ড কেমিস্ট। প্রত্যেকেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স করা এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে ড্রাগ প্রোডাকশনের উপর ট্রেনিংপ্রাপ্ত। প্রত্যেকেই সব ধরনের ড্রাগ তৈরিতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হলেও প্রত্যেকে কাজ করেন ভিন্ন ভিন্ন প্লান্টে। ওরাল এন্টবায়োটিক্স প্লান্টে যারা কাজ করেন, তারা ইনজেক্ট্যাবল এন্টিবায়োটিক্সের প্লান্টে কাজ করেন না। অথচ সব ধরনের ইনফরমেশন মাথায় রাখেন প্রত্যেকেই।
ঠিক একটা ফ্যাক্টরির মতো এমনই ব্যতিক্রমধর্মী, পরিকল্পিত সচেতন কাজের আন্জাম দিচ্ছে কিছু প্রোটিন অনু মাইক্রোস্কোপিক একটা খুবই ক্ষুদ্র জায়গায় একদম কাকতালীয়ভাবে।
আপনি এটি স্বীকার করতে প্রস্তুত? আপনি কেন কোন পাগলও তা স্বীকার করবে না। অথ্চ ঠিক তাই দাবী করছে বিবর্তনবাদীরা।
একটা শুক্রানু দ্বারা একটা ডিম্বানুর নিষিক্ত হওয়া মানেই একটা মানব জীবনের শুরু।
যখন পিতার শুক্রানু দ্বারা মায়ের ডিম্বানু নিষিক্ত হয়, তখন উভয়ের জীনগুলো মিলিত হয় অনাগত শিশুর শারীরিক গঠন কেমন হবে তা ঠিক করার জন্যে। হাজার হাজার জীনের প্রত্যেকটি ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এক একটি জীন ঠিক করে শিশুর গায়ের রঙ, চোখের রঙ, চুলের ধরন, মুখের গড়ন, তার প্রতিটি হাড়ের গঠন, প্রতিটি নার্ভ, গোশতপিন্ড, লিভার, কিডনি এভাবে হাজার হাজার বিষয়।
যখন শুক্রানু মিলিত হয় ডিম্বানুর সাথে তৈরি হয় একটি জীবকোষ, যেটি একজন নতুন মানুষের মূল। ঐ কোষের সাথে তৈরি হয় নতুন একটি ডিএনএ কপি, যা বহন করবে একটি নির্দিষ্ট জেনেটিক কোড, যে কোড বহন করবে অনাগত মানুষটির শরীরের জীবনের বিভিন্ন সময়ের প্রতিটি কোষ।
ঐ নিষিক্ত ডিম্বানুকে একটা মানুষে পরিণত হতে হবে। এ জন্য সেটি সংখ্যাবৃদ্ধি করার জন্য দু’ভাগ হয়, এভাবে প্রতিটি নতুন কোষ ভাগ হতে থাকে। আর ভাগ হওয়ার সময় প্রতিটি কোষই বহন করে সেই একই ডিএনএ কপি, সেই একই জেনেটিক কোড যেন বেশ সচেতনভাবেই।
আবার একই জেনেটিক কোড বহন করলেও কোষগুলোকে পরস্পর পরস্পর হতে ভিন্ন হতে হয়, যার অপর নাম ডিফারেন্সিয়েশন। যে কোষগুলো একটা গোশতপিন্ড তৈরি করবে তাদের হতে হয় একই ধরনের, নিতে হয় এক জায়গায় অবস্থান। যারা তৈরি করবে চোখ, তাদের হতে হয় আরেক রকম, যেতে হয় আরেক জায়গায়। যারা তৈরি করবে হার্ট, তারা হবে আরেক ধরনের এবং এরা চলে যাবে বক্ষগহ্বরে।
কেউ তৈরি করবে চামড়া, ঢেকে দেবে পুরো শরীর।
এরা প্রত্যেক কোষগুচ্ছই পরিমাণমতো সংখ্যাবৃদ্ধি করে, একত্রিত অবস্থান করে আর এভাবেই জন্ম দেয় এক একটি অঙ্গের।
এই যে প্রতিটি কোষের ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গঠিত হওয়া নিয়ন্ত্রন করে ডিএনএ। আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না, ডিএনএ কোন সুদক্ষ বায়োকেমিস্ট নয়, যে সর্বাধুনিক সব যন্ত্রপাতি ও মেশিনারিজ নিয়ে একটা ল্যাবে কাজ করছে কিংবা একটা সুপারকম্পিউটারও নয়, যেটি সেকেন্ডেই মিলিয়ন মিলিয়ন ক্যালকুলেশন করতে পারে। বরং ডিএনএ একটি অনু, যা কতগুলো হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কারর্বন, ফসফরাস, অক্সিজেন পরমানুর সমষ্টি।
এখন আমাদের নীচের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে। একটা মানব শরীরে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন কোষ সংখ্যাবৃদ্ধি করে বিভাজনের মাধ্যমে। এর উপর ভিন্ন ভিন্ন জীনকে ভিন্ন ভিন্ন কোষে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একটিভেইট হতে হয়, যা কোষগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন হতে সাহায্য করে। এবটু গভীরভাবে চিন্তা করে বুঝে নিই, এই যে এতগুলো কোষ ভাগ হচ্ছে, প্রতিটিই কিন্তু বহন করে একটা মানবদেহ তৈরির সমস্ত তথ্য। অর্থাৎ প্রত্যেক কোষই সামর্থ্য রাখে চোখের কোষ, হার্টের কোষ, হাড়ের কোষ, লিভারের কোষ, রক্তের কোষে পরিণত হওয়ার। যদিও প্রতিটি কোষ মানবদেহ তৈরির সমস্ত জেনেটিক তথ্য ধারন করে, কিন্তু এক এক কোষে এক এক সময়ে কেবল কিছু নির্দিষ্ট জীন একটিভ হয়। প্রতিটি কোষ কিডনি তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় জেনেটিক ইনফরমেশন বহন করে, কিন্তু কিডনি তৈরিতে অংশ নেয় কেবল কিছু নির্দিষ্ট কোষ, অন্য কোষগুলো এ কাজে অংশ নেয় না। যেমন লিভারে পাওয়া যায় একটা এনজাইম ‘গ্লুকোজ-৬-ফসফাটেজ’। কেবল লিভারের কোষগুলোই এই এনজাইম তৈরি করে, অথচ এ এনজাইম তৈরির জেনেটিক তথ্য শরীরের অন্য সবকোষগুলোও জানে। চোখের একটা কোষ কখনও এ এনজাইম তৈরি করবে না। ব্রেইনের কোষগুলো কখনও হজম রস তৈরি করবে না, অথচ হজমরস তৈরির জেনেটিক তথ্য তারাও ধারন করে। লিভারকোষগুলো বিষ নিস্ক্রিয় করার কাজেই ব্যস্ত থাকবে, ব্রেইনকোষগুলো তথ্য আদানপ্রদানেই ব্যবহৃত হবে এবং সেভাবেই নিজেকে তৈরি করবে।
এখন কথা হলো, এই যে একই ধরনের জেনেটিক তথ্য বহনকারী কোষগুলোকে কে বললো, এভাবে বিশেষ বিশেষ গঠন নিতে হবে, বিশেষ অঙ্গে গিয়ে বিশেষ কাজ করতে হবে বিশেষ সময়ে? কে তাদের বলেছে এভাবে নিয়ম মেনেই চলতে হবে তাদের। আর কার কথাই বা তারা এভাবে শুনছে, কখনও অন্যথা করছে না?
এটি একদম স্পষ্ট, এমন শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনা কখনোই কো-ইনসিডেন্স ও কাকতালীয়ভাবে হতে পারে না।
কথা এখানেই শেষ নয়। বরং প্রতিটি কোষের প্রতিটি বিশেষ জেনেটিক তথ্য ব্যবহৃত হবে বিশেষ সময়ে। যেমন একজন ল্যাকটেটিং মা এর শরীরেই কেবল দুধ তৈরির সাথে জড়িত জেনেটিক তথ্যগুলো কেবল ঐ সময়েই ব্যবহৃত হবে, অন্য সময়ে নয়। অন্য সময়ে এই জীনগুলো ঘুমন্ত থাকবে।
এই এক্সট্রাঅর্ডিনারি বিষয়গুলোর কোন ব্যাখ্যা বিবর্তনবাদীদের কাছে নেই।
চোখে দেখা যায় না এমন একটা মাইক্রোস্কোপিক জায়গায় মহাপরিকল্পনার সাথে এতগুলো মিলিয়ন মিলিয়ন কাজ সম্পন্ন হচ্ছে কার ইশারায়? কেবলই কাকতালীয়ভাবে?
৮
অফিস থেকে ফিরে ফ্রেস হয়ে সোজা দস্তরখানে পৌঁছে গেলো আশিক।ছোট ছোট ভুনা মাছ আশিকের বড় পছন্দ।সোজা ঐ প্লেটটির দিকেই নজর পড়লো তার। আর নজর ওখানেই আটকে গেলো। হাসির একটা চিকন রেখা ছড়িয়ে পড়লো তার ঠোঁটে।
মাছগুলো প্লেটের উপর এমনভাবে সাজানো হয়েছে, যেন ইংরেজি বর্ণমালার কিছু অক্ষর ফুটে উঠে। সাদা প্লেটে ভুনা লালচে-কালো ছোট মাছগুলো দিয়ে লিখা ‘I LOVE YOU’.
মাছগুলো তো আর এমনি এমনি এভাবে সজ্জ্বিত হয় নি। এ যে সালমারই কাজ!
আশিকদের বিয়ে হয়েছে এক মাস হয় নি। এরই মধ্যে মেয়েটি তাকে কত আপন করে নিয়েছে। আর কত ভাবে নিজের আবেগটুকু জানিয়ে দিচ্ছে বার বার।
‘নাহ! আজই ওকে নিয়ে বেড়াতে যেতে হবে।ছোট খালার বাসায়।
আশিকরা সিএনজি থেকে নামলো।চোখের সামনে সদ্য রঙ করা চারতলা দালান। দালানের সামনে ছোটখাট একটা ফুলের বাগান। বাগানের মাঝামাঝি ঘন, সন্নিবেশিত ফুলের গাছগুলো এমনভাবে কেটে সাইজ করা, তাতে ফুটে উঠেছে বাংলা বর্ণমালার কিছু অক্ষর। সহজেই চোখে পড়ে, তাতে লিখা ‘অবকাশ ‘। অবকাশ খালাদের দালানটিরই নাম।
আশিক ভাবে, আজ দুপুরে মাছের প্লেটের এই সজ্জ্বা, এখানে খালাদের বাগানের চারাগুলোর এই সাজ যেমন বলে দেয়- এর পিছনে রয়েছে কারো নিপুণ হাতের সাক্ষর, ঠিক তেমনই এই আকাশ, এই নদী, এই তরুতলা, এই বৃক্ষ, সর্বোপরি মানুষের ডিএনএ এর এই সচেতন বিন্যাস নিশ্চয়ই কোন একজনের নিপুণ হাতের কারিশমা। আর তিনিই আমাদের স্রষ্টা, আমাদের মহান রব।”
প্রথম প্রথম যখন চীনা ভাষার পত্রিকার কোন পাতা বাজার থেকে জিনিসপত্রের সাথে প্যাকেট আকারে আসতো, দেখে অবাক হতাম। এভাবে, এমন করে প্যাঁচিয়ে লিখে কিভাবে? আর কি বিষয়েই বা লিখা হয়েছে এই পাতায়?
বড় আজব মনে হতো চীনা ভাষার এই বর্ণমালা।
মানুষ যেমন করে কোন বিদেশী ভাষা আয়ত্ব করে, ঠিক তেমনিভাবে বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে আয়ত্ব করছেন ‘ডিএনএ বর্ণমালা’। অবাক হচ্ছেন? না অবাক হওয়ার কিছু নেই। ঠিক একটা ভাষার মতো চারটা অরগানিক বেইসের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মানবদেহের প্রতিটি জীন। অসংখ্য জীন নিয়েইএকটা ডিএনএ। জীন হচ্ছে তার ক্ষুদ্রতম ইউনিট, যা একটা জেনেটিক ইনফরমেশন বহন করে। মানবদেহের এক একটা বৈশিষ্ট্যের জন্য এক একটা জীন দায়ী। কোন জীন নিয়ন্ত্রন করে চোখের রঙ, আবার কোনটা নাকের গড়ন। একটা পেন্টোজ সুগার, একটা ফসফেট, আর একজোড়া অরগানিক বেইস নিয়ে একটা জীন। অরগানিক বেইস হচ্ছে চারটি – এডেনিন, গুয়ানিন, থায়ামিন, সাইটোসিন। এ চারটি বেইসের ভিন্ন ভিন্ন কম্বিনেশন ভিন্ন ভিন্ন ইনফরমেশন ধারন করে। এ চারটি বেইসের প্রথম অক্ষর যেন চার অক্ষর বিশিষ্ট ডিএনএ বর্ণমালা ( A-G-T- C)।বিজ্ঞানীরা ধীরে ধীরে জীনের ইনফরমেশনগুলোর পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হচ্ছেন। অরগানিক বেইসগুলো দেখেই তার চিহ্নিত করছেন এক একটি জীন। এভাবেই লোকেইট করা হচ্ছে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য নির্দেশকারী নির্দিষ্ট জীন। নির্দিষ্ট হচ্ছে বিশেষ ধরনের ক্যান্সারের জন্য বিশেষ জীন। শুধু কি তাই? এক একটা জীনকে আলাদা করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে তা কোন ব্যাকটিরিয়া কিংবা ঈষ্টের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে তৈরি করা হচ্ছে বিভিন্ন হরমোন, ভ্যাক্সিন। আজ যে ডায়াবেটিসের জন্য ইনসুলিন দেয়া হচ্ছে, তা তো এভাবেই তৈরি। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে হুবহু মানুষের শরীরের ইনসুলিনই দেহের বাইরে তৈরি করা হচ্ছে। যদি প্রতিটি জীন প্রতিটি প্রোটিনের জন্য এভাবে ইনফরমেশন সংরক্ষণ না করতো, আর বিজ্ঞানীরা যদি ডাটাব্যাংকের মতো কাজ করা এই ডিএনএ’র ভাষা পড়তে না পারতেন, তাহলে তা কখনও সম্ভব হতো না।
যে কেউ কোন শব্দ কোথাও দেখলে মনে করবে, এর পেছনে কোন লিখক আছেন। কোন ডিজাইন দেখলে ভাববে এর পিছনে কোন ডিজাইনার আছেন। কারণ কিছু ফুলের চারা যেমন নিজে নিজে বিন্যস্ত হয়ে কোন লিখা ফুটিয়ে তুলতে পারে না, ছোটমাছগুলো নিজেরা নিজেরা বিন্যস্ত হয়ে যেমন ‘I LOVE YOU’ লিখা হয়ে যাওয়া অসম্ভব, তেমনই এর চেয়ে বিলিয়নগুন জটিল ইনফরমেশনগুলো ক্ষুদ্রতম একটা স্ট্রাকচারের ভেতরে এভাবে লিখা হয়ে যাওয়া অসম্ভব।
তারপরও কি বলা হবে বিবর্তনের মাধ্যমেই হঠাৎ কাকতালীয়ভাবে এই ঘটনাগুলো ঘটে গেছে, আর সৃষ্টির পর থেকে মিলিয়নবার বার বার ঘটছে? আফসোস, আমার প্রিয় ভাই,
তারপরও তুমি নাস্তিকতার নামে এমন নিপুণ স্রষ্টা থেকে মুখ ফেরাবে?
৯
ধরা যাক, আপনি এখন সুইডেনের স্টকহোমে।
বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার কমিটির মেম্বারদের মধ্যে আপনিও একজন। মিঃ ‘এ’ নোবেলের জন্য এপ্লাই করেছেন। তার টপিক হচ্ছে বিবর্তনতত্ত্ব।
তার সাথে এভাবে কথোপকথন চলছে।
– আপনার কাছে এমন কোন প্রমান আছে যে, অতীতে বিষয়টি ঘটেছে?
– সরি, আমার কাছে নেই।
– ঠিক আছে আপনার কাছে এমন কোন প্রমান আছে বর্তমানে তা ঘটছে?
– আসলে আমি জানি না।
– মিঃ ‘এ’, বিজ্ঞান হচ্ছে কোন ঘটনার প্রমানসিদ্ধ ব্যাখ্যা দেয়া। আপনি আমাদের বলতে পারবেন, বিবর্তন কিভাবে ঘটে? কিভাবে একটা উদ্ভিদ বা প্রাণী ভিন্ন একটা উদ্ভিদ বা প্রাণীতে পরিণত হয়?
– ওয়েল, আমরা মনে করি প্রাকৃতিক নির্বাচন, অতঃপর মিউটেশন এর মাধ্যমে, আসলে ঠিক কিভাবে আমরা তা জানি না।
এখন আপনিই বলুন, আপনি মিঃ ‘এ’ কে নোবেলের জন্য ভোট দেবেন কি?
আসলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ইতিহাসকে কি রি-প্রডিউস করা যায়? যা একবার ঘটে গেছে, তাকে কি পূনরায় তার সমস্ত ধারাবাহিকতাকে অক্ষুন্ন রেখে সংঘটিত করা যায়? উত্তর হচ্ছে, না।
যা অতীতে ঘটেছে একটা দীর্ঘ সময় নিয়ে, সেটিকে কি কোন ল্যাবরেটরীতে পূনরায় শুরু থেকে ঘটানো সম্ভব? একটা ইঁদুরের শরীরে একটা এইড্স ভাইরাস ঢুকিয়ে দিয়ে বার বার তার ফলাফল পরীক্ষা করা সম্ভব। কিন্তু কোন ইতিহাস, যা একবার ঘটে গেছে, সময়টা চলে গেছে, তাকে কি পরীক্ষাগারে পূনরায় টেস্ট করে দেখা সম্ভব? বিবর্তনের বিষয়টিও এমনই।
এ জন্যই বিবর্তনবিদ ও বিজ্ঞানী কলিন পেটারসন পিএইচ,ডি, যা বলেছেন,
“We must ask whether the theory of evolution by natural selection is scientific or pseudoscientific (metaphysical)…taking the first part of the theory, that evolution has occurred, it says that the history of life is a single process of species-splitting and progression. This process must be unique and unrepeatable, like the history of England. This part of the theory is therefore a historical theory about unique events; and unique events are, by definition, not part of science, for they are unrepeatable and so not subject to test..”
তার সারাংশ হলো,
” আমাদের অবশ্যই প্রশ্ন করা উচিত, এই যে বিবর্তনতত্ত্ব, যা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটেছে বলে দাবী করা হচ্ছে, তা কি বৈজ্ঞানিক (scientific), না কি মৃষাবৈজ্ঞানিক (pseudoscientific)? বিশেষ করে সুত্রের প্রথম অংশ – বিবর্তন সংঘটিত হয়েছে, যা ইতিহাসের একটা অংশ, তার কি পূনরাবৃত্তি ঘটানো সম্ভব? যেমন ইংল্যান্ডের ইতিহাস, যা কিভাবে ঘটেছে তা আবার পরীক্ষা করা যায় না। কারন তা ইউনিক, একবারই ঘটেছে, পূনরায় ঘটানো অসম্ভব। তেমনই বিবর্তন একটা ইউনিক ঘটনা, যা পূনরায় ঘটানো অসম্ভব। আর সংজ্ঞানুসারে এটি বিজ্ঞানের অংশ নয়, এজন্য যে তা পূনরায় ঘটানো যায় না এবং টেস্ট করে দেখার মতো কোন বিষয় নয়।
এর অর্থ হলো বিবর্তন কোন বাস্তবতা নয়, বরং একটা হাইপোথিসিস,যা বিজ্ঞান দ্বারা প্রমানিত নয়।
যেমন, বিবর্তনবাদীরা দাবী করেন, বিবর্তন এখনও ঘটে চলেছে, কিন্তু তা এত ধীরে যে, আমরা তা অবজার্ভ করতে পারি না। তাহলে কেউ যদি এ কথা বলে, আমরা বিবর্তন ঘটতে দেখছি না এ কারনেই যে, বাস্তবে বিবর্তন ঘটছে না। এখন তাদের ধারনা এবং এই কথাটির মধ্যে পার্থক্য কতটুকু? একটি সিদ্ধান্ত কি অন্যটির চেয়ে বেশি যৌক্তিক? বিবর্তন ঘটছে, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না, তাই প্রমান করতে পারছি না, এটি তো অনেকটা তেমনই হলো যে, তারা বিশ্বাস করে বিবর্তন ঘটছে। ব্যস এতটুকুই। তাহলে এটিকে কি বিজ্ঞানসম্মত বলা যাবে?
দেখুন, নাস্তিকেরা স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে অভিযোগ করে, তা সরাসরি প্রমান করা যায় না। তাহলে ঠিক একই রকম একটা বিশ্বাসকে কিভাবে তারা গ্রহন করে , যা দলিলবিহীন একটা বিশ্বাস মাত্র। আর তারা এ ব্যাপারে এমনভাবে উঠে পড়ে লেগেছে, যেন নাস্তিকতা একটা নতুন ধর্ম।
আরেকটা বিষয় ভাল করে বুঝতে হবে, বিবর্তনবাদীরা বিবর্তনের পক্ষে প্রমান দিতে গিয়ে বলবে, আজ চাইনীজরা গোল তরমুজকে চারকোনা বানিয়ে ফেলেছে পরিবহনের সুবিধার জন্য, ফলের রঙ পরিবর্তন করা হচ্ছে, ছোট বরই বড় করা হচ্ছে। এ ধরনের আরও কিছু পরিবর্তনের কথা শুনিয়ে দেবে। মনে রাখতে হবে, এগুলো হচ্ছে মাইক্রোইভুলিউশনের উদাহরন, মোটেই ম্যাক্রোইভুলিউশন নয়, যা আমরা আলোচনা করছি। মেথিসিলিন রেজিস্ট্যান্ট স্ট্যাফাইলোকক্কাস অরিয়াস মোটেই ম্যাক্রোইভুলিউশন এর উদাহরন নয়।
মাইক্রোইভুলিউশন অর্থ সামান্য ক্ষুদ্র পরিবর্তন, যা কেবল খুবই ক্ষুদ্র স্কেলে বায়োলজিক্যাল পরিবর্তন আনছে (যেমন রঙ পরিবর্তন হওয়া), যা কখনোই ঐ বিবর্তনের প্রমান নয়, যা তারা দাবী করছে, যেমন, এককোষী থেকে বহুকোষী, এভাবে ছত্রাক, ফাংগাস, এরপর ধীরে ধীরে মাছ, মাছ থেকে উভয়চর, উভয়চর প্রানী থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে এপ্স (অর্থাৎ গরিলা, শিম্পাঞ্জি ইত্যাদি বানর শ্রেনীর প্রানী) এবং অবশেষে এপ থেকে মানুষ।
ম্যাইক্রো-ইভুলিউশনে কেবল পূর্বের জীনের শাফলিং ঘটে, নতুন জেনেটিক তথ্য তৈরি হয় না, জীনপোল আগের মতোই স্থির থাকে।
আর বিবর্তন বলতে বুঝানো হচ্ছে নতুন প্রজাতি তৈরি হওয়া। এক ধরনের প্রাণী বা উদ্ভিদ অন্য ধরনের প্রানী বা উদ্ভিদে পরিণত হওয়া।
মাইক্রোইভুলিউশন কখনোই ব্যাপক বিবর্তনের প্রমান হতে পারে না।
বিবর্তনবাদীদের প্রমানগুলো অনেকটা এমন, গরু ও বিড়াল দুটিরই যেহেতু কান, চোখ, চার পা, শরীরে লোম আছে, সুতরাং উভয়ের পূর্বপুরুষ একই। অথচ স্রষ্টা তো এভাবে কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যের প্রাণীও সৃষ্টি করতে পারেন।
কিছু মানুষ যে মাইক্রোইভুলিউশনকে বিবর্তনবাদের প্রমান মনে করে ভুল বুঝাবুঝির শিকার হচ্ছে, তা বিজ্ঞানী ড্যারেল কট্ঝ (Darrel Kautz) সুন্দর বলেছেন।
“People are misled into believing that since microevolution is a reality, that therefore macroevolution is such a reality also. Evolutionists maintain that over long periods of time small scale changes accumulate in such a way as to generate new and more complex organisms… This is sheer illusion, for there is no scientific evidence whatever to support the occurrence of
biological change on such a grand scale. In spite of all the artificial breeding which has been done, and all the controlled efforts to modify fruit flies, the bacillus escherichia (e-coli), and other organisms, fruit flies remain fruit flies, E-coli bacteria remain E-coli bacteria, roses remain roses, corn remains corn, and human beings remain human beings.”
” মানুষকে এভাবে ভুল বুঝানো হচ্ছে যে, মাইক্রোইভুলিউশন যেহেতু বাস্তবতা, সেহেতু ম্যাক্রোইভুলিউশনও বাস্তবতা হওয়া উচিত। বিবর্তনবাদীরা বলছে, লম্বা সময় ধরে ছোট পরিবর্তনগুলো একত্রিত হয়েই অবশেষে নতুন ও জটিল জীবের উদ্ভব ঘটছে। কিন্তু এটি একটি নিছক ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। কারন এর পক্ষে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমান নেই যে, এত বিশাল একটা স্ককেলে এ ধরনের বায়োলজিক্যাল পরিবর্তন সম্ভব। বর্তমানে যত ধরনের কৃত্রিম ব্রিডিং ঘটানো হচ্ছে এবং নিয়ন্ত্রিত প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ফল, ই-কলাই ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য প্রানীর ক্ষেত্রে, সব গুলোতে ফল ফলই থাকছে, ই-কলাই ব্যাকটেরিয়া ই-কলাই থেকে যাচ্ছে, গোলাপ ফুল গোলাপই থেকে যাচ্ছে, শস্য শস্যই থেকে যাচ্ছে, মানুষ থেকে যাচ্ছে মানুষ।
আর যখনই আপনি বিবর্তনবিদদের লিখা পড়বেন, আপনি দেখবেন তারা এভাবে লিখছেন, ‘বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন’, ‘আমরা মনে করি’, ‘হতে পারে’, ‘সম্ভবত’ ইত্যাদি। আর স্বাভাবিকভাবেই হাইপোথিথিস লেভেলে এভাবেই বলা হয়, যা দ্বারা বুঝা যায়, বিবর্তনকে বিজ্ঞানীদের দ্বারা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত থিওরি বলার সময় এখনও আসে নি। আপনি অবাক হয়ে লক্ষ করবেন, আমাদের দেশের নাস্তিকেরা, যেমন অভিজিত, বন্যা আহমেদ ;তাদের লিখায় এ বিষয়গুলোকেই এভাবে লিখেছেন ‘আমরা এখন জানি’।
একেই বলে ধোকাবাজি। যে কোন ভাবে নিজেদের নতুন ধর্মবিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মিথ্যা ও ধোকাবাজির আশ্রয় নেয়া।
কম সতর্ক ও বিজ্ঞান সম্পর্কে খুবই কম পূঁজি নিয়ে যারা বিজ্ঞান অধ্যয়ন করে, তারাই এদের দ্বারা ধোকাগ্রস্ত হয়।
যুগ যুগ ধরে মানুষ একই ঘটনা দেখে আসছে। গরু থেকে গরু হওয়া, ছাগল থেকে ছাগল হওয়া, কলাগাছ থেকে কলাগাছ হওয়া, আমগাছ থেকে আমগাছ হওয়া, মানুষ থেকে মানুষ হওয়া। একবারের জন্যও তার বিপরীত কিছু প্রত্যক্ষ করে নি।
এর বিপরীতে এইচআইভি ভাইরাসের দ্রুত মিউটেশনের মাধ্যমে তার বিরুদ্ধে কোন ড্রাগকে ইফেক্টিভ হতে না দেয়া, কিংবা ব্যাকটিরিয়ার এন্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে রেসিস্ট্যান্ট তৈরির মাধ্যমে অকার্যকর করে দেয়া নিঃসন্দেহে মিউটেশনের মাধ্যমে নিজেকে পরিবর্তনের উজ্জ্বল দৃস্টান্ত। কিন্তু কখনোই তা ব্যাপক বিবর্তনের উদাহরন নয়।
বিবর্তনবাদীরা যেটি বলছেন, লক্ষ লক্ষ বছরে এলোমেলো পরিবর্তনের মাধ্যমে সমস্ত জটিল জীব তৈরি হয়েছে সেই এককোষী জীব থেকে- কি পরিমাণ একটা নেশাগ্রস্ত কল্পনা, তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।
যদি বলা হয়, এর পক্ষে আপনাদের দলিল কি?
রিচার্ড ডকিন্সের ভাষায় তারা বলবেন, আরে এর পক্ষে সব তথ্যই তো পৃথিবীতে আছে। আমরা কেবল চৌকষ গোয়েন্দার মতো দুইয়ে দুইয়ে চার মিলাচ্ছি।
তার যুক্তি হলো, অপরাধী যখন একবার অপরাধ করে ফেলে, তা তো দ্বিতীয়বার রি-প্রডিউস করা যায় না। কিন্তু আলামতগুলো বিশ্লেষণ করে ঠিকই একজন ডিটেকটিভ তা নির্ণয় করে ফেলেন। তেমনই বিবর্তন তো হয়েই গেছে, আমরা ফসিলগুলো বিশ্লেষণ করে নিখুঁতভাবে বলে দিচ্ছি।
একটু বিষয়গুলি তুলনা করুন তো!
কোথায় সদ্য ঘটে যাওয়া অপরাধের আলামত আর কোথায় লক্ষ লক্ষ বছর আগের কিছু হাড় বা পায়ের ছাপ নামের ফসিল, যেগুলির উপর দিয়ে বয়ে গেছে কত চড়াই উৎড়াই।
বিবর্তনবাদীরা ফসিলগুলো বিশ্লষণের সময় কত যে কাল্পনিক চিত্র আঁকেন তার ইয়ত্তা নেই। কোন জীবাস্মের পাশে কিছু পাথর পড়ে থাকলে ব্যস তারা পাথরের ব্যবহার জানতো! কিন্তু তারা যে কাপড় পড়তো না, উলঙ্গ থাকতো, তা কি জীবাস্ম দেখে বুঝা যায়? তারা যে আলাদা প্রজাতি ছিলো, তা বুঝার উপায় কি।প্রজাতির সংজ্ঞা যেটি জীববিজ্ঞানীরা দিয়েছেন, নিজেদের মধ্যে যারা প্রজননে সক্ষম। আদিম মানুষের ফসিল বলে যে হাড়গুলোকে দাবী করা হচ্ছে, সেগুলো যে ভিন্ন প্রজাতির মানুষ তা নিশ্চিত হওয়া যাবে কিভাবে? কেবল বলে দিলেই হলো?
মাছ থেকে উভয়চর, উভয়চর থেকে সরীসৃপ, সরীসৃপ থেকে এপ্স, এপ থেকে মানুষ। প্রমান কি? যেহেতু তাদের ডিএনএতে নব্বইভাগের কাছাকাছি মিল। ব্যস মিল থেকেই বুঝা যায়, তাদের পূর্বপুরুষ একই।কি হাস্যকর যুক্তি।
একজন স্রষ্টা প্রতিটি জীবকে আলাদাভাবে সৃষ্টি করেছেন। তাদের মাঝে রেখেছেন কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য। এমন যে নয়, তা প্রমান করবেন কিভাবে?
আসলে কোন প্রমান নেই। কেবল একটা অন্ধবিশ্বাস, কেবলই জোর করে একটা মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা।
১০
ছোট ভাইটির বুদ্ধিসুদ্ধি কম, সহজে কোন বিষয় বুঝতে পারে না। সেবার ও,টি,তে কি কান্ডটাই না সে ঘটিয়েছে।
হানিফ সাহেবের পায়ে গ্যাংগ্রিন হয়েছে। সার্জন সাফ বলে দিয়েছেন পা’টি কেটে ফেলতে হবে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়। নইলে তাকে বাঁচিয়ে রাখা টাফ হবে।
হানিফ সাহেবকে ও,টি,তে ঢুকানো হয়েছে। পাগল ছোটভাইটি কিভাবে যেন বিষয়টি জেনে গেলো। এরপর সে কি আর দেরি করতে পারে! বড়দাকে যে সে খুবই ভালোবাসে।
এক দৌঁড়ে সে ও,টি,র ভেতরে। কেউ তাকে রুখতে পারে নি। গিয়েই হানিফ সাহেবের হাত ধরে টানাটানি শুরু করেছে। নাহ, কিছুতেই সে পা কাটতে দেবে না। সার্জনের সাথে তার সে কি ঝগড়া!
তাকে কোনভাবেই বুঝানো যাচ্ছিলো না। সার্জনকে সে এভাবে শাঁসালো,
” আপনার এত সাহস! একটা মানুষের পা কেটে ফেলবেন! কেমন জালিম আপনি! একটা মানুষকে পঙ্গু করে দেবেন!”
তাকে বুঝানোর চেষ্টা করা বৃথা। ছোটবেলা থেকেই হাবা এই পাগলটিকে কিভাবে বুঝানো যাবে! তার কেবল এক কথা,
“কিছুতেই পা কাটা যাবে না। এ যে মহা জুলুম! আর তাছাড়া বড়দাকে যে সে বড় ভালোবাসে।”
শেষে আর কি করা। তাকে টেনে হিঁচড়ে ও,টি, থেকে বের করা হলো।
আসলে ব্রেইনের সীমাবদ্ধতা একটা মহা সমস্যা। যে প্রোগ্রাম ব্রেইনে ঢুকানো নেই, তা কিছুতেই বুঝে আসবে না। যে সফ্টওয়্যার কম্পিউটারে ঢুকানো হয় নি, সেটির সাথে সংশ্লিষ্ট কোন প্রোগ্রাম কম্পিউটারটিতে চলবে না, এটিই স্বাভাবিক।যতই বলা হোক, এটি সুপারকম্পিউটার। তাতে কি! প্রোগ্রামটি করা থাকতে হবে তো! আর সুপারকম্পিউটার যত সুপার হোক, তার একটা লিমিটেশন আছে। এক পর্যায়ে সে থেমে যাবে। মানুষের ব্রেইনও ঠিক তেমনই। এরও একটা লিমিটেশন আছে।
যে সর্বোচ্চ বিশের নামতা পর্যন্ত জানে, বীজগনিত কখনও ধরেও দেখে নি, সে কিভাবে বীজগাণিতিক কোন সমস্যা সমাধান করবে?
উপরে ব্রেইনের সীমাবদ্ধতার একটা উদাহরণ দেয়া হলো। মেধার স্বপ্লতার কারনে পা অপারেশন করাকে জুলুম ভাবা হচ্ছে। তেমনই মেধা অপরিপক্কতার কিছু উদাহরণ নীচের লাইনগুলোতে দেখুন।
“কোন ব্যক্তি যদি একজন ক্ষুধার্তকে অন্নদান করে ও একজন পথিকের মাল লুন্ঠন করে, একজন জলমগ্নকে উদ্ধার করে ও অন্য কাউকে হত্যা করে, অথবা একজন গৃহহীনকে গৃহদান করে এবং অপরের গৃহ করে অগ্নিদাহ, তাহাকে ‘দয়াময়’ বলা যায় কি? হয়তো তাহার উত্তর হইবে -‘না’। কিন্তু উপরোক্ত কার্যকলাপ সত্ত্বেও ঈশ্বর আখ্যায়িত আছেন দয়াময় নামে।……”
এরপর আপনি কুরআনের নীচের আয়াতগুলো পড়ুন,
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كلا،
মানুষ, যখন তার রব তাকে পরীক্ষা করার জন্য সম্মান দিয়ে দেন, নিয়ামত বাড়িয়ে দেন, সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন। আর যখন পরীক্ষা করার জন্যে তার রিযককে সংকুচিত করে দেন, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে হেয় করেছেন। কখনও তেমন নয়। ”
সংশয়বাদী আরজ আলী মাতবর তার মনে উদয় হওয়া কিছু প্রশ্নকে এভাবেই প্রকাশ করেছেন। তিনি যদি কুরআন ও হাদীসের দিকে ফিরতেন, তার এ সব প্রশ্নের উত্তরের জন্য যদি কোন বিজ্ঞ আলিমের শরণাপন্ন হতেন, তবে সহজেই তিনি সঠিক উত্তর পেয়ে যেতেন। আফসোস! তার সে সৌভাগ্য হয় নি। তিনি আসলে তার বইগুলোতে কিছু প্রশ্নের জবাব খুঁজেছেন। প্রশ্নগুলোর যে জবাব নেই এমন নয়। তবে জবাবের জন্য নিজের সীমাবদ্ধ মেধাকেই যথেষ্ট ভাবা বঞ্চিত হওয়ার অনেক বড়ো কারন।
স্রষ্টা তো কেবল স্রষ্টা নন, তিনি মালিকও। ধরে নিন, আমার দুটি মোরগ আছে। তার একটিকে আমি জবাই করে দিলাম, অন্যটিকে রেখে দিলাম। এ ক্ষেত্রে কি কখনও এ প্রশ্ন আসবে, আমি কেন এক মোরগের উপর জুলম করলাম, অন্যটিকে ছেড়ে দিলাম? বরং মানুষের সর্বোচ্চ আদালতও এ কথা বলবে, আমি এ ব্যাপারে স্বাধীন। অথচ আমি মোরগদুটির স্রষ্টা নই।
তাহলে যিনি স্রষ্টা, যিনি মালিক, তাঁর উপর কিভাবে জুলমের প্রশ্ন আসবে?
এর উপর যদি পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তো আর কোন প্রশ্নই নেই। যদি সাময়িক পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে কিছুদিন কাউকে কষ্টের মধ্যে রাখেন, এরপর অনন্তকালের জন্য তাকে চিরস্থায়ী সুখ দিয়ে দেন, তবে এটিকে কে জুলুম ভাববে?
মানুষ ভিডিওগেম তৈরি করে। গেমগুলোতে কতকিছু ঘটে যায়, কোনপক্ষ জিতে, কোনপক্ষ হেরে যায়, ধ্বংসও হয়ে যায়। যে ভিডিওগেম খেলছে, এতে তার কিছু যায় আসে না। তেমনই স্রষ্টা তার যেমন ইচ্ছা পৃথিবীতে পরিবর্তন ঘটান, চাই সাপ ব্যাঙকে গিলে খাক, চাই বাঘ হরিণ শিকার করে খাক, এতে মানুষের প্রশ্ন করার সুযোগ কোথায়? এ সব অহেতুক প্রশ্ন করে লোক হাসানোর কি অর্থ হতে পারে? স্রষ্টাকে জালিম সাব্যস্ত করা, কিংবা দয়াময় হিসেবে স্বীকার না করার অজুহাত হিসেবে এগুলো কতই না দূর্বল যুক্তি। স্রষ্টা খুবই ভালো করে জানেন, কেন তিনি এ সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। জুলম কোনটা, দয়া কোনটা সেটিও তিনিই ভালো করে জানেন। যার জুলম ও ইনসাফের মাপকাঠিই ঠিক নেই, সে কিভাবে জুলুম ও দয়ার মাঝে পার্থক্য করবে? সে তো দয়াকেও জুলম ভাববে, যেমন পাগলাটে ভাইটি পা অপারেশনকে জুলম ভেবেছিলো।
আসলে স্ব-অধ্যয়নে শিক্ষিত আরজ আলী মাতবরের জ্ঞানার্জনে রয়ে গেছে অনেক ফাঁক। ফলে তিনি মিস করেছেন অনেক কিছু, বুঝতে ভুল বুঝেছেন অনেক বিষয়। আর নিজের প্রশ্নগুলোর উত্তরও তালাশ করেন নি ঠিক জায়গায়।
আর তার এ সমস্ত অজ্ঞতাই আজ নব্যনাস্তিকদের জন্য পাঠ্যপুস্তক। তাই তো অভিজিতদের লেখায় ঘুরে ঘুরে আসে আরজ আলি। যারা নিজেকে হঠাৎ করে মুক্তচিন্তক হিসেবে দেখাতে চায়, তাদের হাতেও দেখা যায় ‘আরজ আলি মাতবর’।
১১
কতই না অদ্ভূত আমাদের এই চোখ! যখনই চোখের গঠন নিয়ে ভাবি, দৃষ্টির রসায়ন নিয়ে চিন্তা করি, আমার ভেতরটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নুইয়ে আসে।ইচ্ছে করে এক সিজদায় জীবনটা কাটিয়ে দিই।
কী আশ্চর্য গঠনই না আমাদের এই চোখের।চল্লিশের অধিক বৈচিত্রপূর্ণ অংশ নিয়েই এই আঁখিযুগল।এর মধ্যে মাত্র একটির অবস্থাই যদি আমরা বিবেচনা করি, বুঝে আসবে কোন জিনিসের নাম সৃষ্টিকৌশল।
আমাদের চোখের বৈচিত্র্যময় একটি অংশ লেন্স। যে বিষয়টি আমরা কখনোই উপলদ্ধি করি না, এই যে চোখের সামনের প্রতিটি বস্তুকে আমার সুস্পষ্ট দেখা, তা যে এই লেন্সটির অবিরাম স্বয়ংক্রিয় ফোকাসিং এরই ফসল।
চোখের সামনে আমার আঙ্গুলের অগ্রভাগ ধরলাম।এক দৃষ্টিতে তাকালাম আঙ্গুলটির অগ্রভাগে।অতঃপর সেখান থেকে দ্রুত দৃষ্টিকে সরালাম সামনের দেয়ালে। আবার দ্রুত নজর করলাম আঙ্গুলে।দৃষ্টির প্রতিটি পরিবর্তনে আমরা অনুভব করি সুক্ষ্ণ এক দ্রুত এডজাস্টমেন্ট।
লেন্সটি মাইক্রোসেকেন্ডেরও কম সময়ে তার পুরুত্বকে পরিবর্তন করছে। আর লেন্সের পুরুত্বের এই পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতগুলো পেশি। এরা দ্রুত সংকোচিত ও প্রসারিত হয়ে লেন্সটিকে এডজাস্ট করে নিচ্ছে যেন সামনের বস্তুটি আমার কাছে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।লেন্সটি এভাবে নিজের পুরুত্বকে এডজাস্ট করছে আমাদের জীবনের প্রতিটি সেকেন্ডে।আর কোন প্রকার ভুল করছে না একবারও।
ফটোগ্রাফার যখন ছবি তোলে, প্রতিবার হাতের মাধ্যমে নিজেদের ক্যামেরার এই এডজাস্ট তারা করে নেয়।কখনো কখনো তাদের সঠিক ফোকাসের জন্য কিছু সময় রীতিমতো যুদ্ধ করতে হয়। বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তি এমন ক্যামেরা উদ্ভাবন করেছে, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফোকাসিং করতে পারে। কিন্তু কোন ক্যামেরাই চোখের মতো এত দ্রুত ও এত সঠিকভাবে ফোকাস করতে পারে না।
একটা চোখ কেবল তখনই দেখতে সক্ষম, যখন চল্লিশেরও বেশি অংশ একই সময়ে একসাথে সঠিকভাবে কাজ করে।চোখের লেন্স সেই অংশগুলোর মাত্র একটি।
যখন চোখের প্রতিটি অংশ- কর্নিয়া, আইরিশ, পিউপিল, রেটিনা, অক্ষি-পেশিগুলো সবাই একসাথে সঠিকভাবে কাজ করছে, কিন্তু কেবল আইলিড (নেত্রপল্লব) অনুপস্থিত, তবে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে চোখের বিশাল ক্ষতি হয়ে যাবে আর সে কাজ করা বন্ধ করে দেবে। সবই ঠিক আছে, কেবল অশ্রু তৈরি হওয়া বন্ধ হয়ে গেলো, চোখ শুকিয়ে যাবে এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যে অন্ধ হয়ে যাবে।
উপরের কথাগুলো সংক্ষেপ করলে যা দাঁড়ায়, তার অর্থ হলো, একটা জটিল অঙ্গ, যা অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন অংশের সমন্বয়ে কাজ করে, তার একটিকেও যদি সরিয়ে নেয়া হয়, সেই সিস্টেমটি অকেজো হয়ে পড়বে। এই বিষয়টিকে বায়োকেমিস্ট মাইকেল জে বিহে তার বিখ্যাত বই ” Darwin’s black box: the biochemical challenge to evolution’ ( প্রকাশ ১৯৯৬) এ বর্ণনা করেছেন ‘হ্রাস-অযোগ্য জটিলতা’ নামে।তার এই বই ছিলো ডারউইনবাদের উপর বিশাল আঘাত।
লেন্স, রেটিনা, পিউপিল, কর্ণিয়া ইত্যাদি অনেকগুলো জটিল অঙ্গ কিভাবে একসাথে হঠাৎ করে গঠিত হবে কেবলই প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে? কারন প্রাকৃতিক নির্বাচন তো আলাদাভাবে ভিজুয়াল নার্ভ ও রেটিনাকে বেছে নিতে পারে না। ধরে নিলাম হঠাৎ করে লেন্স গঠিত হলো, কিন্তু রেটিনার অনুপস্থিতিতে এর কি অর্থ হবে? কাজেই দেখার জন্যে এই সবগুলো অংশের একসাথে ডেভেলপ করাকে কোনভাবেই এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।
১২
চোখের সামনে ফুলে-ফলে সুশোভিত বাগান।রজনীগন্ধার মিষ্টি সুবাসে মনটা উতলা।পাখির কিচিরমিচির ডাক কানে আলোড়ন তুলছে।দখিনা হাওয়ার ঠাণ্ডা পরশে যেন স্বর্গীয় স্বাদ। চেয়ারে গা এলিয়ে চোখ বন্ধ করে আস্বাদনের চেষ্টা।আহা! কতই না প্রাণময় আজকের এই সকালটা।
কিন্তু আমরা কি জানি, আমি এই যে জীবন্ত চারপাশটা দেখছি এ কেবলই আমার ব্রেইনের কিছু পারসেপশন? আমার চোখ মোটেই এই জীবন্ত বাগানকে দেখছে না।বরং আমার চোখের রেটিনায় পড়েছে এই বাগানের একটা দ্বি-মাত্রিক ছবি। রেটিনার রড আর কোন কোষে কিছু ক্যামিক্যাল রিয়্যাকশন হয়ে তৈরি হয়েছে একটা ইলেকট্রিক সিগন্যাল, যা গিয়ে আঘাত করছে ব্রেইনের ছোট্ট একটি জায়গায়, যার নাম ভিশন এরিয়া।সেখানে ইলেকট্রিক সিগন্যালগুলো এনালাইসিসের মাধ্যমে তৈরি হয়েছে একটা চিত্র।
এটি কেবল দেখার ক্ষেত্রে নয়, বরং আমাদের শুনা, আমাদের ঘ্রাণ নেয়া, আমাদের স্বাদ আস্বাদন, আমাদের স্পর্শ এভাবে আমাদের প্রতিটি অনুভবই কেবল ব্রেইনের কিছু ইলেকট্রিক সিগন্যালের এনালাইসিস পরবর্তী চিত্র।
যা বললাম, তা কোন দার্শনিক উক্তি নয়, বরং আধুনিক বিজ্ঞান দ্বারা প্রমানিত বাস্তব সত্য।
আমি খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। বাগানের একটা দৃশ্য আমার নজরে পড়ল। আমি মনে করছি বাস্তব বাগানটিকেই আমি দেখছি। আসলে এভাবেই আমরা চিন্তা করতে শিখেছি। অথচ আমার দেখা বলতে আমার চোখের সরবরাহ করা কিছু ইলেকট্রিক সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে ব্রেইনের পিছনে তৈরি হওয়া একটা চিত্র।
তাহলে ব্যাপারটি কি দাঁড়ালো? আমার দেখা প্রকৃত দেখা নয়। আমার শুনা প্রকৃত শুনা নয়। এভাবে আমার ধরা, আমার নাকের ঘ্রাণ নেয়া, আমার জিহ্বার স্বাদ চেখে দেখা। বস্তুর প্রকৃত রূপটি আমার উপলদ্ধির বাইরে। আমার ইন্দ্রিয়গুলো যতটুকু তথ্য ব্রেইনকে ইলেকট্রিক সিগন্যাল হিসেবে সাপ্লাই দিয়েছে, ব্রেইন কেবলই তার একটা চিত্র তৈরি করেছে। কাজেই আমি বাইরের জগতটা দেখছি না, বরং আমার ব্রেইনের পিছনভাগে তৈরি হওয়া একটা কপি দেখছি।
আমাদের ব্রেইন প্রোটিন এবং চর্বির তৈরি একটা নিরেট জায়গা। সেখানে কোন আলো পৌঁছে না, কোন শব্দ পৌঁছে না। কেবল কিছু সিগন্যাল পৌঁছে। যে আকাশকে আমি নীল দেখছি আসলেই কি তা নীল? যে গাছের পাতাগুলি আমি সবুজ দেখছি তা কি আসলেই সবুজ? একজন কালার-ব্লাইন্ড রঙগুলো এভাবে সনাক্ত করতে পারবে না।
এর মানে কি দাঁড়ালো?
আমার বাইরের এই যে জগত, তার প্রকৃত রূপ আমরা কখনও দেখি নি। দেখার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু একজন আছেন, যিনি প্রকৃতই এই জগতটাকে দেখেন, যিনি দেখার জন্যে কোন চোখের মুখাপেক্ষী নন।
আশ্চর্য হলো, সেই আমরাই, যারা কোন বস্তর অরিজিনালটাকে দেখি নি কখনও, তারাই স্রষ্টাকে উপলদ্ধি করতে চাই। অথচ আমরা জানি না বাইরের এই জগতটার আসল রূপটা কি। আমার ইন্দ্রিয়গুলোকে দেয়া সামর্থ্য অনুসারে যতটুকু তথ্য তারা ইলেকট্রিক সিগন্যাল আকারে ব্রেইনে পাঠাচ্ছে, তার আলোকেই সেখানে তৈরি হচ্ছে একটা অবয়ব। আর আমরা তাই দেখছি। হয়তো এমনও হতে পারে প্রতিটি বস্তুর মাঝে রয়েছে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য যা ধারণ করার ক্ষমতা আমাদের ইন্দ্রিয়ের নেই। ফলে আমরা তা কোনদিন জানতে পারবো না।
আমরা যদি আমাদের এই সীমাবদ্ধতাকে বুঝতে পারি, তাহলে সবার কাছে পরিষ্কার হবে, স্রষ্টাকে এই ইন্দ্রিয়গুলো দিয়ে উপলদ্ধি করা, তার থাকা না থাকার সিদ্ধান্ত দেয়া কেবলই স্বর্ণ মাপার নিক্তি দিয়ে হিমালয় ওজন করার মতো। কিংবা বিষয়টি এরও অনেক উর্ধ্বে। হিমালয় মাপা কিংবা স্বর্ণ মাপা দুটোই তো ইন্দ্রিয়গুলোর উপলদ্ধির ভেতরের জিনিস। কিন্তু স্রষ্টা, যিনিই একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানী, সমস্ত বস্তুর বাস্তবতাকে জানেন, তিনি তো অবশ্যই আমাদের ইন্দ্রিয়ের উপলদ্ধির উর্ধ্বে হবেন।
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار .(سورة الأنعام.
হে আল্লাহ! প্রকৃত রাস্তা তুমি আমাকে দেখাও। আমি যেন পথভ্রষ্ট না হই।
১৩
আমরা আসলে আমাদের স্রষ্টাকে চিনি নি। বরং আমার খাহেশাত আমাকে আমার রবের ব্যাপারে ধোকায় ফেলেছে। নফসের এই ধোকার চুড়ান্ত পর্যায় হলো অবিশ্বাস। সে অবিশ্বাস দূর করার উপায় হলো নফসের খাহেশাতের টুঠি চেপে ধরা। ফিরে আসার কাহিনীগুলো তা’ই বলে। আমার এক ভাইকে আমি এমনই পেয়েছিলাম।
ভাইটি নামাজে খুব কাঁদছিলেন। এই কান্না কোন অভিনয় ছিলো না। এই কান্না হককে উপলদ্ধির কান্না, নিজের অতীতের জন্য অনুশোচনার কান্না। সেদিন হোস্টেল মসজিদের দু’তলায় নামাজের কাতারে আমিও ছিলাম। জামাতটি এসেছিলো চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ইউনিভার্সিটি থেকে। ভাইটি ওখানে পড়েন। তিনি কিছুদিন আগেও নাস্তিক ছিলেন। সদ্য অন্ধকার থেকে আলোয় ফিরেছেন কিছু দরদী দাঈ’র আন্তরিক প্রচেষ্টায়। নাস্তিকতা থেকে ফেরা এমন অনেককেই আমি দেখেছি। বিশ বছরের অধিক একটা সময় দাওয়াতের কাজে জড়িত থাকার সুবাদে এমন অনেকের সাথে দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন সময়ে গাশত করতে গিয়ে সংশয়-সন্দেহে পতিত কতজনের সাথেই না আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। এই লম্বা সময়ের অভিজ্ঞতা থেকে তৈরি হয়েছে নাস্তিক ও নাস্তিকতা সম্পর্কে আমার নিজস্ব একটা ভিউ।
কয়জন মানুষই বা ভালো করে পড়ে, বুঝে নাস্তিক হয়? নাস্তিকদের কয়জনের অবস্থান এ সম্পর্কে বিস্তারিত পড়াশুনা ও পর্যবেক্ষণের পর? নাস্তিক হওয়ার পেছনে আকলের দাসত্ব এবং প্রবৃত্তির দাসত্বের মাঝে কোনটির ভূমিকা বেশি? আমার মনে হয়েছে অধিকাংশই আকলের উপর প্রবৃত্তির প্রাধান্যের কারনেই নাস্তিক হয়। তাদের প্রবৃত্তি তাদের আকলকে নিয়ে খেলে। কিন্তু প্রবৃত্তির এই খেলা এতটাই সুক্ষ্ম, তারা তা উপলদ্ধি করতে পারে না। তারা তাদের সিদ্ধান্তটিকে আকলের কনক্লোশন মনে করে, কিন্তু বাস্তবে তা তাদের প্রবৃত্তিরই খেল। তাই যখনই কোন কারনে প্রবৃত্তির এই প্রাবল্য প্রশমিত হয়, তাদের আকলের উপর প্রবৃত্তির এই দখল হালকা হয়, তখন আকল তার স্বাভাবিক গতিতে কাজ শুরু করে, এক পর্যায়ে নিজের সিদ্ধান্তের অসারতা তার নিজের কাছেই স্পষ্ট হয়ে যায়।
ধরা যাক, একজন খুব পড়ে, বুঝে নাস্তিক হয়েছে। এখন যদি আপনি পাল্টা যুক্তি, তত্ত্ব এবং তথ্য দিয়ে তাকে পরাভূত করতে পারেন, যদি বুঝাতে পারেন তার অবস্থানের ভিত্তি নিতান্তই দূর্বল, সে সৎ হলে সহজেই ফিরে আসবে। কিন্তু যারা নাস্তিক হয়েছে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে, প্রবৃত্তির লাগামহীন খাহেশাত চরিতার্থ করতে গিয়ে নাস্তিকতাকে কেবল সে একটা অবলম্বন হিসেবে গ্রহন করেছে, তাকে হাজারো যুক্তি, তত্ত্ব, তথ্য দিয়ে ফেরানো যাবে না। সে এক পয়েন্টে হেরে আরেক পয়েন্ট সামনে নিয়ে আসবে, ঘুরে ফিরে নিজেকে নিজের অবস্থানে ধরে রাখতে সচেষ্ট থাকবে । তার প্রবৃত্তি তাকে পরাজিত হতে দেবে না। এটি মোটেই তার বুঝ বা জ্ঞানের গভীরতার কারনে নয়, কেবলই প্রবৃত্তির দাসত্ব ধরে রাখার এক প্রবণতা থেকে।
এই ধরনের এক জুনিয়রের সাথে একবার আমার কথা হচ্ছিলো। স্কুলে তার পজিশন খুব ভালো ছিলো না। পড়াশুনায় একদম পেছনের সারির না হলেও মাঝারি ক্যাটাগরিরই ছিলো। এমনিতেই বেসিক সায়েন্স ও ম্যাথের উপর আমাদের দখল কমই থাকে! স্বাভাবিকভাবে তার অবস্থাও এর ব্যতিক্রম ছিলো না। তার সাথে আমার তর্ক হচ্ছিলো। তার ফিরতি জবাবগুলো শুনে আমার বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিলো না বেসিক সায়েন্সে তার দখল কতটুকু। কিন্তু আমি দেখছিলাম কিভাবে সে প্রসঙ্গের পর প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে নাস্তিক সেলিব্রেটিদের বিভিন্ন লেখা থেকে ধার করা বিভিন্ন বেপরোয়া উক্তি করে যাচ্ছিলো, যা বিতর্কের স্বাভাবিক গতি অনুসরণ করে নয়। মনে হচ্ছিলো ইসলামের প্রতি বিদ্বেষমূলক এই সব পয়েন্ট তুলে ধরতে পেরে সে এক ধরনের বিকৃত স্বাদ অনুভব করছে। তার মাঝে না ছিলো সত্য কবুলের আগ্রহ, না ছিলো সততা।
আমাদের দেশের ছাত্রছাত্রীদের অধিকাংশই যে কোন বিষয়ে গভীর ও বিস্তৃত স্টাডি করে খুবই কম। পেশাগত জীবনে যতটুকু প্রয়োজন হয় এর বাইরে খুব বেশি বিস্তৃত অধ্যয়নের সুযোগ সবার হয় না। আমাদের ডাক্তারদের একটু বেশি পড়তে হয়, সারাজীবন পড়তে হয় – এমন একটা কথা প্রচলিত আছে। কিন্তু এই পড়াশুনাও কিন্তু ঠেকায় পড়ে, পেশাগত প্রয়োজনে, না পড়ে উপায় থাকে না বলে। দুয়েকজন ব্যতিক্রম তো সবসময়ই থাকেন।
আজ নাস্তিকতা যে সব পয়েন্টকে মূল ধরে আগাতে চাচ্ছে তা কোয়ান্টাম ফিজিক্সই হোক কিংবা ইভোলিউশন থিওরী, এর প্রত্যেকটিই গভীর, সিস্টেমিক, বিস্তৃত অধ্যয়নের দাবী রাখে। কেবল ভাসা ভাসা দু’চারটা বই বা লিটারেচার পড়ে নিয়েই একটা ইনফারেন্স টানা, অন্তত স্রষ্টা থাকা না থাকা টাইপ কনক্লোশন টানা এতো সহজ নয়। কেন সহজ নয় সংক্ষেপে বলি। প্রথমত স্রষ্টা থাকা না থাকা এটি কোয়ান্টাম ফিজিক্স বা ইভোলিউশন থিওরী কোনটারই আলোচ্য বিষয় নয়। প্রশ্ন হবে, তাহলে এর ভিত্তিতে এই প্রশ্ন উঠে আসে কি করে! উত্তর ঘুরে ফিরে ঐ আগেরটি, প্রবৃত্তি তাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এখানে নিয়ে যায়, যাওয়ার পথটি অমসৃণ এবং অসম্ভবের কাছাকাছি পর্যায়ের জটিল হওয়া সত্ত্বেও জোর করে প্রবৃত্তি তাকে ওখানে নিয়ে যেতে চায়।
আস্তিকতা নাস্তিকতা একটা পুরাতন বিতর্ক। যেদিন থেকে ‘নফস’ ‘খোদা’ হতে চাওয়ার ইচ্ছে করতে শুরু করেছে, সেদিন থেকেই এই বিতর্কের শুরু। যা সৃষ্ট, তার একজন স্রষ্টা থাকবেই একদিকে এই সুস্পষ্ট সত্য, এর বিপরীতে স্রষ্টা ছাড়াই এই বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে তা প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা। দৃঢ়ভাবে যেহেতু তা প্রমাণের পথ বন্ধ, তাই এর বিকল্প বা কাছাকাছি কিছু প্রমান করতে পারলেও তারা খুশি। যদি কেবল এতটুকু বলা যায় “স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন, এটি যেমন একটি সম্ভাবনা, স্রষ্টা ছাড়াও বিশ্বজগত সৃষ্টি হওয়া সম্ভব এটিও একটি সমান সম্ভাবনা।” তাই যখন কোন বৈজ্ঞানিক থিওরী থেকে ঠিক এই ধরনের কোন অনুসিদ্ধান্তের নাগাল তারা পায় একেবারে লাফিয়ে উঠে। স্টিফেন হকিং যখন দ্য গ্রান্ড ডিজাইন বইয়ে কোয়ান্টাম ফিজিক্সের উপর ভিত্তি করে অংকের কঠিন মারপ্যাঁচ শেষে বলেন, কোয়ান্টাম ফিজিক্সের ভিত্তিতে স্রষ্টা ছাড়াও বিশ্বজগত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাব্যতা ব্যাখ্যা করা যায়, তখন তারা এটিকে অকাট্য প্রমান জ্ঞান করে একেবারে ময়দানে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু অংকের এই কঠিন মারপ্যাঁচ তারা নিজেরা আদৌ বুঝে নিয়েছে, নাকি নিজের প্রবৃত্তির চাহিদার সাথে মিলে যাওয়ার কারনে তার অন্ধ উচ্চারণ শুরু করে দিয়েছে মাত্র। দুয়েকজন না হয় বুঝে চিল্লানো শুরু করলো, কিন্তু বাকীরা? কারণ যে অঙ্ক নিজেই হিসাব কষে বুঝে নেয়া সম্ভব হয় না, তার উপর নির্ভর করে আত্মিক প্রশান্তি কখনোই অর্জিত হওয়ার নয়। আর যদি হয়ও, শেষ পর্যন্ত প্রবেবিলিটির দুই প্রান্ত কেবল সমান হলো, উভয়টির মাঝে একটিকে প্রাধান্য দেয়ার মীমাংসাকারী কই? শেষ কথা, এর দ্বারা তাদের আল্টিমেট লক্ষ্য অর্জিত হয় না। কিন্তু প্রবৃত্তির ঘোড়াকে সন্তুষ্ট করার একটা অবলম্বন তারা খুঁজে পায় বৈকি!
সম্ভাবনা তাহলে কেবল দুটি। স্রষ্টা বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন, স্রষ্টা ও সৃষ্টি – এই সহজ যোগসুত্র, এর বিপরীতে আরেকটি সম্ভাবনা – স্রষ্টা ছাড়াও সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। কিন্তু কোনটি আসলে হয়েছে? এটি অতীত। সুত্র দিয়ে বা অঙ্ক কষে প্রমাণ করার জিনিস নয়।
বিবর্তনবাদ নিয়েও একই কথা। বিবর্তনবাদীরা ঠিক একই ধরনের একটা অনুসিদ্ধান্ত টানতে চায় যে, “স্রষ্টা ছাড়া বিবর্তনবাদের মাধ্যমেও মানুষের উৎপত্তি হতে পারে”। কিন্তু এভাবেই মানুষের উৎপত্তি হয়েছে এ কথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা কঠিন। সর্বোচ্চ কেবল এতটুকু দুই সম্ভাবনার পাল্লা সমান বা কাছাকাছি দাবী করার একটা সুযোগ সৃষ্টি হওয়া । বিবর্তনবাদ টিকে গেলে কেবল এতটুকু বলা যাবে যে স্রষ্টা ছাড়াও মানুষের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দেয়া যায়। এর মাধ্যমে প্রবৃত্তিপুজায় একটু বাতাস করা গেলে তো লাভই হলো!
সোজাকথায় কোন প্রবৃত্তিপুজারী নাস্তিককে আপনি শুধু তাত্ত্বিক খন্ডনের মাধ্যমে নাস্তিকতা থেকে ফেরাতে পারবেন না। বাকী রইলো তাত্ত্বিক খন্ডনের আবশ্যকতা। এই আবশ্যকতা কেউ অস্বীকার করবে না।
আমার এক স্যার ছিলেন। ছাত্রজীবনে একবার তিনি নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলেন। ফলে হালাল-হারামের সব ধরনের বাছবিচার ছেড়ে দিয়েছিলেন। ধর্মকে বিসর্জন দিতে চেয়েছিলেন জনমের মতো। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তিনি এক মোল্লার হাতে পড়েছিলেন। মোল্লা কি তাকে তাত্ত্বিক খন্ডনের মাধ্যমে ফিরিয়েছিলেন? মোটেই নয়। মোল্লার বিশ্বাসের দৃঢ়তা, চারিত্রিক পরিশুদ্ধি, ইখলাস, দিলভরা দরদের আহবান তিনি উপেক্ষা করতে পারেন নি। ঐ আলিম তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, ” তুমি কি প্রিন্সেস জরিনার নাচ দেখেছো? ‘ তখন প্রিন্সেস জরিনার নাচ বড় বিখ্যাত। স্যার স্বাভাবিকভাবেই হ্যাঁ শব্দে জবাব দিয়েছেন। তিনি বললেন, ” তোমার তা কেমন লাগে? ‘ স্যার বললেন, খুব ভালো লাগে। মোল্লা বললেন, খুব ভালো লাগাটা কেমন? খুব ভালোলাগা ব্যাখ্যা করার জন্য আর কোন শব্দ স্যারের ভান্ডারে ছিলো না। স্রষ্টার স্রষ্টা কে? এ চক্র ভাঙ্গার জন্য ঐ আলিম এই উদাহরণের অবতারণা করেছিলেন।
স্যার আমাদের বলেছেন, ‘ আমি এর চাইতে কঠিন পর্যায়ের তর্ক এই টপিকে করেছি। কিন্তু সেদিন হুজুরের চোখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু বলার শক্তি আমি খুঁজে পাই নি। সব ধরনের পাল্টা যুক্তির বদলে কেমন যেন লজ্জা, অনুশোচনা আমাকে চেপে ধরেছিলো। আমার মনে হতে লাগলো, তাঁর অন্তরের ইস্পাতকঠিন এই দৃঢ়তার মুকাবিলা করার মতো সাহস ও শক্তি আমার দূর্বল অন্তরে নেই। আমি বললাম, হুজুর! আমাকে কালিমা পড়ান, আমি তাওবা করছি।’
নাস্তিকতা থেকে ফিরে আসা এমন ভাইদের সাথে কথা বলে দেখেছি, তাদের সিংহভাগই তাত্ত্বিক কোন খন্ডনের কারনে ফিরেছেন এমন নন। তাত্ত্বিক খন্ডন হয়তো পরবর্তীতে প্রশান্তি যুগিয়েছে, কিন্তু ফেরার মূলে বিশ্বাস ও চরিত্রের দৃঢ়তাসম্পন্ন মুখলিস দাঈগনের বারংবার দিলভাঙ্গা আহবান। সেখানে যুক্তির চেয়েও কল্যানকামিতা ও দিলের দরদের ভূমিকা বেশি ছিলো। নিজের অভিজ্ঞতায়ও দেখেছি, এই ধরনের সঙ্গীন মূহুর্তগুলোতে যখনই ‘ইন্নাকা লা তাহদী মান আহবাবতা’ অন্তরে জাগরুক থেকেছে, ফলে নিজের তাত্ত্বিক আলোচনাগুলোকে আল্লাহপাকের ইচ্ছার সামনে নিস্ক্রিয়,অসহায় মনে হয়েছে, সেখানেই দাওয়াত প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে। আর যেখানেই দিল হাকীকত থেকে গাফেল ছিলো, সেখানে সুন্দর তাত্ত্বিক আলোচনাও কোন উপকার করে নি।
ফিরে আসার কাহিনীগুলোতে বরাবরই নীচের বিষয়টি কমন। জীবনে অপ্রত্যাশিত কোন ধাক্কা, বা কোন প্রিয়জনকে হারানোর মূহুর্ত কিংবা কোন আল্লাহওয়ালার কাঙ্ক্ষিত বা অনাকাঙ্ক্ষিত সাহচর্য, অথবা মুজাহাদাপূর্ণ খালিস দ্বীনি দাওয়াতের কোন কাফেলায় সামান্য সময় অতিবাহিত করার বরকতে যখনই প্রবৃত্তির লাগাম কিছুটা হলেও হালকা হয়েছে, অথবা আকল কিছুটা হলেও প্রবৃত্তির দখল থেকে মুক্ত হয়েছে, তখনই আকল ফিরে পেয়েছে ভাবনার সঠিক গতিপথ। খুব কম সময়েই সে ফিরে এসেছে নাস্তিকতা থেকে। হঠাৎ ক্যাম্পাস থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বিড়াতিত হওয়ার ধাক্কায় নাস্তিকতার ভুত ছাড়তে তো আমরা নিজের চোখে দেখেছি। তবে বাস্তবেই তারা নাস্তিক ছিলো কিনা সেটি অন্য প্রশ্ন। প্রকৃতই কেউ আসলেই নাস্তিক হতে সক্ষম কিনা তা আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তবে ধাক্কা খেলে অনেকেই ফিরে আসে, আসতে বাধ্য হয়। সব দৃঢ়তায় একদিন চিড় ধরে।
মুসলিম পরিবারের ছেলে নাস্তিক হয় কেন? হবে না’ই বা কেন? যখন শৈশবে ঈমানের সঠিক তারবিয়াত হয় নি, আখিরাতের অনিবার্য বিষয়গুলো হৃদয়ে পোক্ত হয়ে গাঁথে নি, তখন বয়ঃসন্ধিকালের সেই বিদ্রোহী মূহুর্তে যখন শরীয়তের নানা হুকুম কেবল প্রবৃত্তির উত্থাল ঘোড়াকে থামাতে চেয়েছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই দ্বীন হয়ে উঠেছে অপ্রিয়। চারপাশে যখন কেবল ভোগ করার, প্রবৃত্তির লাগামহীন চাহিদা মেটানোর উন্মুক্ত হাতছানি, তখন ধর্মের এই অর্গল স্বাভাবিকভাবেই অপ্রিয়, অযৌক্তিক মনে হবে। সময়ের আবর্তনে প্রবৃত্তির চাহিদার কেবল ব্যাপ্তি বেড়েছে, মন হয়ে পড়েছে আরও বিদ্রোহী, তাই এক পর্যায়ে বাধা সরানোর সামান্য খড়কুটোও হয়ে পড়েছে অবলম্বন। প্রবৃত্তির লালায়িত জিহ্বা আকলকে করে ফেলেছে অকেজো। প্রবৃত্তির এই লাগামহীন চাহিদাই যখন নাস্তিকতার আঁতুড়ঘর, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার প্রশমনই হবে এই ভুত ছাড়ানোর উপায়। যেখানেই তা ধাক্কা খাবে, যেখানেই অনুভব হবে জীবনের রূঢ় বাস্তবতা, সেখানেই প্রবৃত্তির প্রভাববিহীন আকলের সঠিক চিন্তা তাকে মূহুর্তেই বের করে আনবে অবিশ্বাসের অন্ধকার থেকে। যে গতিতে সে অন্ধকারের দিকে ছুটছিলো, একশ’ আশি ডিগ্রী ঘুরে এর চেয়ে তীব্রগতিতে সে ফিরবে আলোর দিকে।